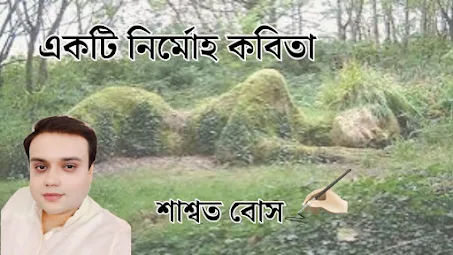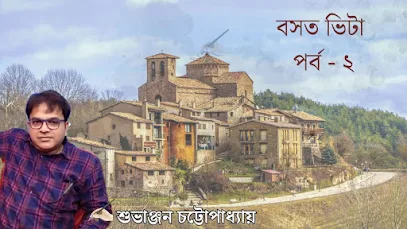শনিবার, ২০ জুলাই, ২০২৪
কবিতাভিত্তিক
বিভ্রম
মধুপর্ণা বসু
চোখ জুড়ে শুধু অতীতের সুর্মাদানী গলে পড়ে,
তাকে ডাকি অদ্ভূত বিস্মৃত নাম নিয়ে, যা ছিলনা
তবুও সেই নাম জপমালা হল কেন?
আসল তলিয়ে গেছে হাজার টেথিসের সুনামি ওপারে,
ভালোবাসি একটা অস্তিত্বে, সেই সত্যি সেই-ই চাক্ষুষ।
বাকি আধা জন্ম অনতিক্রম্য, শুধু ঝাপসা ওপেক,
তার মধ্যে দিয়ে অচেনা নিজেও,
শুধু আজকের সেই ডাক সত্যি!
কত তর্কে, কত ইজেল ভেঙে গুঁড়ো হল ঠাণ্ডা যুদ্ধে,
মনের সাথে আত্মার,তার সাথে স্পর্শ প্রিয় অস্তিত্বের,
আর তারও পরে...
অজানা গহীন কালো থেকে তুলে আনা প্রাণ শব্দ,
সেই আজ পরিচয়ের থেকেও বড় সত্যি-
যা মাথার ধূসর বস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও বিস্ময়
ভুলে যাওয়া অতীতের তলহীন কুয়া থেকে উঠে
বর্তমানকে কি এক অবুঝ টানে জড়িয়ে আছে।
কবিতাভিত্তিক
শব্দ কথার সম্পর্ক
শুভাদিত্য ঘোষ দস্তিদার
জীবনে কথার চেয়ে শব্দ খুবই অবশ্যম্ভাবী
কথার প্রেক্ষিতে ফোটা শব্দগুলো
ভালো - মন্দে মেশানো,
কিন্তু শব্দ জেগে থেকে
বিস্তৃত করে রাখে পাতা
আক্রমণ হতে পারে যে কোনোদিন
সম্পাদকের কলমের।
মাতৃসমা শব্দ যদি
তুমুল বিস্তার নিয়ে আসে কখনও
আমার খুব আনন্দ হয়,
আমি দেখতে পাই রূপসী যত কথা
কথার রকমারি আস্ফালন দেখে
আমার বড় হিংসে হয়,
কথা তো মানুষের মধ্যেই জেগে থাকে
সমাজ সংসারে জীবনে সর্বত্র।
কবিতাভিত্তিক
দুটি জীবন
তাপস মাইতি
মুখর পদধ্বনি ব'য়ে গেলে থেমে যায় ঝড়
গাছেরা বুঝি তখন আলোকিত হয়
অনেক পথ চলা চারদিকে
আবার মেঘ ওঠে
ঝড় তাহলে কি ফের সম্ভবনাময়
অথচ প্রকৃত প্রেমিকেরা আসেনি এখনও
ঝড়ের বদলে উঠলো বজ্র- বিদ্যুৎ
গানের সুরে পথ কাদা করছে বর্ষা
ফিরে যায় সকল পথচারী
কেবল দুটি জীবন বেড়িয়ে পড়েছে
খুঁজতে সেই গাছেদের পাড়ায়
যেখানে অন্ধকার জ্বালবে একটি প্রদীপ
কবিতাভিত্তিক
খুকি ও পাখিওয়ালা
হারাধন ভট্টাচার্য্য।
"পাখি পুষবেন গো,পাখি," হাঁক দেয় পাখিওয়ালা
ডাক শুনে দোতলার গবাক্ষ থেকে দেখে মধুবালা।
"ও পাখিওয়ালা,দাঁড়াও,শুনতে পাচ্ছ,পাখিওয়ালা"/ পাখিওয়ালা চমকে ওঠে,- কে ডাকে কোন্ সে বালা!
পুরনো রাজবাড়ী, সিংহদরজা সামনে ছোট্ট মেয়ে-/ পাখিওয়ালা অবাক চোখে,তারই চোখে রইল চেয়ে,
স্বর্ণচাঁপা গায়ের বরণ, মুখ খানি তার পরীর গড়ন
কোন্ দেবকন্যা,মায়াভরা কাজল কালো দুটি নয়ন।
"ও পাখিওয়ালা, কী কী পাখি দেখাও না একবার "
কাছে গিয়ে পাখিওয়ালা,শোনায় তার পাখি-বাহার।
জয়"এই দেখ টিয়া, চন্দনা, বুলবুলি, ময়না,শ্বেতকবুতর
আর কী পাখি নেবে, তুমি চাইলে খুঁজব তেপান্তর।
"তোমার খাঁচার সব পাখিই নেব,কত দাম বলো চটপট,
দেখ না ওরা নীল আকাশে ওড়ার জন্য করছে ছট্ফট্,/ ডাকছে ওদের নীল আকাশ,ডাকছে ঐ সবুজ বনতল "
বলল খুকি, পাখিওয়ালা শূন্যে তাকায়, চিন্তায় বিহ্বল।
"এ তো অনেক দাম, তুমি কি কিনতে পারবে ও মেয়ে, বিনি পয়সায় একটি পাখিই তোমায় দিলাম তার চেয়ে"
বলেই পাখিওয়ালা চাইল খুকির চোখে।
বলল মধুবালা
"সব পাখির দাম হবে না, দিই যদি এই সোনার বালা?"
"তোমার হাতের সোনার কঙ্কন,আমি নেবে কেমন ক'রে
ওর দাম তো অনেক টাকা,ও খুকি যাও গো ঘরে ফিরে"
বলল পাখিওয়ালা।
"এ বালা লাগে না কোনো কাজে, পাখিগুলোকে দাও গো ছেড়ে, ভীষন কষ্ট খাঁচার মাঝে,/
মাকে ছেড়ে ওরা কি থাকতে পারে, ওদের মা'রা কাঁদে
বলো, তোমায় যদি কেউ ফন্দি ক'রে,বন্দী করে ফাঁদে।"
বলেই খুকি বাড়িয়ে দিল হাতের সোনার বালাখানি ---
ছোট্ট খুকির কোমল কথায় কি ভাবল,বলল,"মামণি
তোমার সোনার বালা আমার পাখির চেয়েও দামি
ওটা তোমারই থাক, ওটা না হয় তোমায় দিলাম আমি,
সব পাখিই তোমায় দিলাম, মুক্ত করো নিজের হাতে উড়িয়ে দাও ওদের নীল আকাশে, ভাসুক আনন্দেতে।/ তোমার জন্য চিরতরে ছেড়ে দিলাম পাখি ধরার কাজ,
তোমার কাছে শিখে নিলাম মুক্তির আনন্দ কি দরাজ!
নীল আকাশে ডানা মেলে পাখিরা গাইল কতো গান
খুকি ও পাখিওয়ালা রইল চেয়ে আনন্দ বিহ্বল প্রাণ।
কবিতাভিত্তিক
মনে পড়ে
বিশ্ব প্রসাদ ঘোষ
স্বপ্নের মধ্যে দীঘল রাজহাঁস
আর দীঘল কিছু দেখলেই
মনে পড়ে যায় সুজাতার কথা।
যে নারী বুদ্ধকে পায়েস দিয়েছিলেন,
অন্য কিছু বোধহয় নয়, তাহলে
বুদ্ধদেবের বাকি জীবনটা অন্যরকম হতো_
কবিতাভিত্তিক
বোকামো
আসিফ আলতাফ
কিছু কিছু বোকামো আমার কড়ে আঙ্গুল ধরে হাঁটে,
এতো বকাঝকা করি
এতো রাগঝাক
তবু নাবালক সন্তানের মতো ওরা আমার আঙুল ধরেই থাকে;
আপনাকে দেখলে একটি বোকামো
কপোলে ঝুলে থাকা চুল ফু দিয়ে উড়িয়ে দেয়
আমি ওর কান্ড দেখে হেসে উঠি
আপনার দু গালে রং ধনু ওঠে;
একটি বোকামো আপনি হাসলে আমকে বিব্রত করে
তখন কী করবো কিছুই বুঝি না;
আপনি সামনে এলে একটি বোকামো
আমার প্রপোজ ফ্লাওয়ার নিয়ে দে ছুট
তার কারণে আপনাকে একটি টকটকে লাল গোলাপ দিয়ে
আজো বলা হয়নি
আই লাভ য়্যু ....
কবিতাভিত্তিক
ভোকাট্টা হবার অপেক্ষায়
উদয়ন চক্রবর্তী
এসো হাঁটতে হাঁটতে আমরা কিছু কথা বলি
ম্যাজেন্ডা রঙের হৃৎপিন্ডে যেন রক্তকরবীর
ছোঁয়া না লাগে
যেন জার্মান প্রাচীর তৈরি না হয় সম্পর্কের সাঁকোয়
ভাই সুপারি না দেয় ভাইয়ের জন্য
তারপরও আমরা না চাইলেও গ্রহণ লাগবেই
সম্পর্কের ছায়া ক্রমশ অন্ধকার ছড়িয়ে নিজের রক্ত মাংস চিবিয়ে খাবে
আর আকাশ তার নিজস্ব খেলায় মেতে থাকবে
তার সংসার নিয়ে
আমরা হয়ত শকুন হয়ে দূর আকাশে
খুঁজে দেখব কোথায় মৃত বিবেক চিৎ হয়ে শুয়ে
এখনও প্রাণ আছে কিনা
মানুষের অমানুষি ক্লোন ঘুরে বেড়াবে
ঘরের ভেতর রাস্তা বাজার আর নগরদর্পণে
আমরা সবাই এখন রাজা
সবাই আমরা আততায়ী
একটা বেচাল একবজ্ঞা পেটকাটি ঘুড়ির
বেয়াদপি জীবন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে
আমরা হারিয়ে ফেলছি নিজস্ব ঠিকানা
শূন্যহাতে আসা গন্ত্যবহীন যাত্রাপথে হঠাৎ
ভোকাট্টা হবার অপেক্ষায় বসে আছি
ওদিকে আমার আত্মজ স্বপ্নের রামধনু হাতে
পেরিয়ে যাচ্ছে নিজস্ব সাঁকো।
কবিতাভিত্তিক
হেমন্তের রূপকথা
জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
এবারও হেমন্ত হঠাৎ চলে গেল।আলতো ছোঁয়া যে পাইনি
এমন নয়,খানিক হাওয়া শিমুলের লাল,কিছুটা পলাশ আঁকড়
ঘেঁটু বা বুনোফুল দু-একটা ছোবল মারেনি এমনও নয়
তবু একটাও দীর্ঘ স্মৃতিকথা লিখিনি।
কোনো চাষি বা মজুরের ঘামে আগুনফুল আঁকিনি
প্রহরের পাখিডাক বা গোধূলির ছবিও লিখিনি।
হেমন্ত হারিয়ে গেল।হেমন্ত মানে সেই অনাথ ছেলেটির সঙ্গে
বাসন্তীর দেখা হয়েছিল,আলাপ ও প্রলাপে স্কুল আর
কোচিং ক্লাসের ঘণ্টায় কোনো রামধনু কেউ তো দেখেনি
স্কুল সেরে বাসন্তীর পতিগৃহে যাত্রার পরপরই হেমন্ত উধাও !
শান্ত পুকুরের মতো গাঁয়ে ঢেউ উঠেছিল, স্বচ্ছজল,কাদা নয়,
ছেলেটা সবার প্রিয়,বড়ো ভালো, মেয়েটিও।
তবু হেমন্ত হারিয়ে গেল,হেমন্তেরা এভাবেই হারিয়ে যায়।
তার মায়ের চুলে পাক ধরেছে,ছোটো হয়েছে দীর্ঘশ্বাস
বিকেলের কাজ সেরে দরজা খুলে বসে সে ভাবনায় ডুবে থাকে
দিনের আলো কমে এলে রাতের আলো জ্বলে,
তার চোখের চিকচিক স্বপ্ন আরও উজ্জ্বল হয়।
তাতে অলৌকিক অক্ষরে লেখা হারানো মানিক লাভের
অনবদ্য রূপকথা।
কবিতাভিত্তিক
চিয়ার্স
সুমন্ত দাশ রায়
আগের মতো মেঘ করেনা এখন।
কেমন যেন শুকনো আছে জমিন!
'বৃষ্টি' নামে ডাকলে তোমায় পাবো?
তোমার ফোনে অধরা ইনকামিং।
মেসেঞ্জারে দেখছিনা আজ কেন?
'শরীর খারাপ'? আজ কুড়ি দিন হলো।
আগের মাসের তারিখ মনে আছে,
সেদিনতো ফোন তুললে! আজ তোলো।
কী যেন এক বলার ছিলো কথা।
ভুলেই গেছি যা কিছু দরকারি।
আমার চোখে খুচরো পাপের বোঝা
তোমার চোখের কাজলে আন্তরিক।
বাতাসে আজ ধাক্কা খাচ্ছি অনেক।
মদ ধরিনি, অ্যালকোহলের কসম।
তবুও নেশায় মত্ত আছি এমন _
পারলে এখন আদিম হিসেব কষো।
মিটিয়ে দেবো পুরোনো ধার বাকি,
বকেয়া সুদ, থোড়াই করি কেয়ার!
মেঘকে নাহয় ডাকপিওনের বেশে
পৌঁছে দেবো জানলাতে, মাই-ডিয়ার।
অথৈ জলে তল পাবেনা জেনেও
ঘাটের কাছে নিজের ছায়া ঘাঁটি।
ছায়ার বুকে তরঙ্গ দাও বলেই
নিয়ম করে জলের ধারে হাঁটি।
তোমার ছবি দেবো কি নিউজ-ফিডে?
ব্লক না হওয়ার নিয়ম নীতি মেনে।
ইথার ঘিরে জমতে থাকে ব্যথা।
আবার ভাবি -কী লিখবো ক্যাপশানে?
আচ্ছা ছাড়ো... যে কথা বলছিলাম_
এই হ্যাংওভার থাকুক স্মরণীয়।
একলা হয়ে ছাদের ধারে এসে
আকাশকে আজ 'চিয়ার্স' বলে দিও।
কবিতাভিত্তিক
এই যেমন জড়িয়ে আছি
সায়ন চক্রবর্তী
এই যেমন জড়িয়ে আছি
সুতোর সাথে সুতোর মতো
পায়ের চেনা জুতোর মতো
আদর আর ছুতোর মতো-
এই যেমন জড়িয়ে আছি।
হঠাৎ করে বিশ্বজুড়ে
তেমন কিছু করা হবেনা
আমার কবিতা পড়া হবেনা
বিরাট কিছু গড়া হবেনা
হঠাৎ করে বিশ্বজুড়ে।
তবুও এমন এক এক দিনে
এই শহরেই ফিরে দাঁড়াবো,
তোমাদের প্রেমে ঘিরে দাঁড়াবো
আঁধারের বুক চিরে দাঁড়াবো
তবুও এমন এক এক দিনে।
এই যেমন জড়িয়ে আছি
তোমায় প্রেমে জড়িয়ে নিয়ে
শিশুকে কোলে ছড়িয়ে নিয়ে
বাঁচার নেশায় জরিয়ে নিয়ে
এই যেমন জড়িয়ে আছি।
কবিতাভিত্তিক
অতল হিয়া
সৌরভ ভাদুড়ী
গভীরে ডুব, মনখারাপী হাওয়া
আকাশ বুকে ঝুলছে একাই চাঁদ,
তোমার বুকে কে জানে কোন ছায়া
গোপন প্রেমিক , পাতছে কি কেউ ফাঁদ?
কান্না? সে তো ভৌমজলের মতন
খুঁড়লে বুকে বের হয়ে ঠিক আসে
পথ হারিয়ে ভ্রান্ত কোনো পথিক
পতঙ্গ যে আগুন ভালবাসে |
আগুন পোড়ায়, জলও ডোবায় জানি
ডোবায় তোমায় নষ্ট ভালবাসা ?
হিমেল রাতই চাঁদকে ধরে রাখে
মরার আগেও মিথ্যে কাছে আসা !
স্রোতের ভাঁটা টানবে আবার হাত,
অতীত তোমায় দেবেই মরণ ডাক
চোরাবালি কিংবা নবীন ভোর
ঘুম জমেছে, আজ এটুকুই থাক...
কবিতাভিত্তিক
একটি নির্মোহ কবিতা
শাশ্বত বোস
মরা নদীর জলে ডুব চান, বড় ভয়|
এখনই রেডিওয় পিকিং ভেসে আসে|
পৃথিবীটা এখন খসা চামড়ার দাদে ভুগছে|
গোলাপি মরুভুমি কবির কল্পনা
ছেড়ে, শরীরী ব্ল্যাকহোলে পাড়ি জমায়|
পেণ্ডুলামি প্রজাতন্ত্রে চতুষ্পদী পোকারা,
দেশভাগ ভুলে বনসৃজনে মাতবে|
স্বাস্থ্যবান পিরামিডের, মহাজাগতিক জ্যামিতিকাল,
এখন অভিযোজনের উলম্বপাতে,
ধরা দেয়| স্যাটায়ারে উলঙ্গ অপুষ্টি,
উদার ঊরু, গভীর যোনি, কিংবা নিরম্বু আপীন|
ধ্বংসের বুকে পা দিই আমি|
পরাগমোচনে মেয়েলি নক্ষত্রযাপন,
দীর্ঘ অনুচ্ছেদের রুমাল বেয়ে,
গান্ধর্বীর ধূসর মাইলফলক|
পৃথিবী আসলে, একটি মেয়ের নাম|
সম্মিলন
হাল-হকিকৎ
সৈকত মাজী
1.
ভাতা নাও
গুন গাও,
ম্যানিফেস্টো জুড়ে, শ্রী-এর মেলা।
হারিয়ে হুঁশ,
করি দিলখুশ,
আমাদের নিয়ে চলে খেলা।
2.
গরম হাওয়া
আকাশ ছোঁয়া,
ফি মাসে হেডলাইন মুদ্রাস্ফীতি।
গরিবের উনুনে
চাল চড়ে অনটনে,
রেপোরেটে ছাড় পায় ব্যাংক কটি।
3.
শ্রম ফেরি
আমরা করি,
ঘর ছেড়ে, বহুদূরে পরবাস।
পরিজন পরিবার,
বুকফাটা হাহাকার,
এসেছি জোটাতে দু'মুঠো ভাত।
4.
ফোটে কাশ
বাড়ে আশ,
শিল্প হবে তার বালিশে।
দেখো আনাচে কানাচে
উন্নয়ন চপ ভাঁজে,
মশকরা শুধু শুধু নালিশে।
5.
পদখালি ইস্কুলে
শিক্ষা তলায় অতলে,
শিরদাঁড়া ভেঙে দিলো কে?
যোগ্যরা রাস্তায়,
পচন ধরেছে শিক্ষায়,
নতুন সকাল আসবে কবে?
নিবন্ধ
কবিতার ভাল-মন্দ
শ্রীমন্ত সেন
প্রাক্ কথন
কবিগুরু তাঁর ‘ঐকতান’ কবিতায় লিখেছিলেন, ‘শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ’। দুঃখের বিষয় আজকাল সেই ভঙ্গিসর্বস্ব কবিতা লেখার প্রবণতা বড় উৎকটভাবে দৃশ্যমান। এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত কাব্যজগতের অনুসন্ধানে আমাদের অবশ্যই ব্রতী হতে হবে। এখানেই কবিতার ভাল-মন্দ নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তাই আজ বাইশে শ্রাবণে কবিগুরুর মহাপ্রয়াণদিবসে সেই আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক। তাঁকে স্মরণের মাধ্যমে এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করে নিজেই ধন্য হই।
প্রথমেই স্বীকার করি যে আমি সেই অর্থে কবি নই, তবে আমি বরাবরই কাব্য সরস্বতী-র এক নগণ্য অনুরক্ত মাত্র। যেহেতু সারস্বত অঙ্গনে প্রাণের টানেই পড়ে আছি এবং বয়সও কম হয়নি, তাই কবিতা কী, কোনটা ভাল কবিতা ও কোনটাই বা খারাপ কবিতা—সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট না হলেও একটা অস্পষ্ট ধারণা অন্তত হয়েছে। উপরন্তু সারস্বত পত্রিকা ‘কবিতার আলো’-র সন্নিধানে এসে সেই কিঞ্চিত হলেও ধারণা-ঋদ্ধ হয়েছি। সেই ধারণাকে সম্বল করেই আমার আজকের এই আলোচনা। মনে হতেই পারে যে এ অনধিকারীর আলোচনা—হতেই পারে। আমি প্রথমেই তাই মাফ চেয়ে নিচ্ছি।
‘কবিতার আলো’-র পর্যবেক্ষণ
এ কথা অনস্বীকার্য যে আজকাল কবিতা প্রচুর পরিমাণে লেখা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের বেশির ভাগই ‘কবিতা পদবাচ্য’ নয়। কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছেন –‘সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।’ যে সব তথাকথিত কবিতা লেখা হচ্ছে তাদের বেশ কিছু বিবৃতি, প্রতিবেদন বা রিপোর্টিং মাত্র, যা সাংবাদিকের কাজ, কবির নয়। কিছু কিছু তথাকথিত কবিতা তো স্লোগান ছাড়া কিছুই নয়।
আবার কিছু ছন্দোময় কবিতার নামে ছন্দোহীন বা ছন্দসামঞ্জস্যহীন রচনা। তেমনই কিছু কবিতা ‘আধুনিক গদ্যকবিতা’-র নামে যথেচ্ছাচার, তা না কবিতা না গদ্য। মনে রাখতে অনেকেই ভুলে যান যে গদ্য কবিতায় চাক্ষুষ ছন্দের দোলা না থাকলেও, অন্তর্লীন ছন্দস্পন্দন তো থাকারই কথা, যেমন রবীন্দ্রনাথেরই গানে আছে ‘নয়নসমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই’। এ ছাড়া ভাবসৌন্দর্যের দোলা তো থাকেই।
একটি অনলাইন পত্রিকার ঘড়ি বিষয়ক লেখা আহ্বানের প্রেক্ষিতে এক কবি লিখলেন ঘড়ির আকার, অবয়ব, তার কী কী যন্ত্রাংশ থাকে অর্থাৎ কটি কাঁটা ইত্যাদি, যুগে যুগে তার আকারের বিবর্তন প্রভৃতি নিয়ে কবিতা। আর একজন লিখলেন—
মহাকালের ঘড়ি
এখানে সময় দ্যাখে আপনার মুখ,
এখানে ক্রমশ জমে দুরাশার ছায়া,
এখানে সময় রাখে সব সুখ-দুখ,
এখানে প্রতি পদে আগামীর ছায়া।
পিছুটান ভেঙে চলা মানুষের মাপে,
উৎসুক বিশ্বের অফুরান ডাক,
মহাকাল জেগে থাকে নিমেষের খাপে,
নশ্বর জীবনের সীমানা ছাড়াক। (মাত্রাবৃত্ত ছন্দে)
প্রথম কবিতাটি একটি প্রতিবেদন বা রিপোর্ট ব্যতীত কিছুই নয়। কিন্তু দ্বিতীয় কবিতাটি কবিতায় সময়কে ধরে রাখতে সক্ষম হল। মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক রচিত হল। ‘পিছুটান ভেঙে চলা মানুষের মাপে।’ … ‘মহাকাল জেগে থাকে নিমেষের খাপে’। যা নিয়ে কবিতা, তাকে ছাড়িয়ে অন্যমাত্রায় পৌঁছে যাওয়ার মধ্যেই কবিতার সার্থকতা—নিমেষ তখন শাশ্বতে পরিণত হয়।
উল্লেখ্য যে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় বলা হয়েছিল-- সামনে একটি শুকনো কাঠ পড়ে আছে—এই ভেবে মুখে মুখে একটা শ্লোক রচনা করতে। এক কবি বললেন, ‘শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে (‘তিষ্ঠতি+অগ্রে’) -–মানে ‘সামনে একটি শুকনো কাঠ পড়ে আছে’। তিনি আক্ষরিক অর্থে ভাবকে কবিতায় ধরলেন। আর মহাকবি কালিদাস বললেন, ‘নীরসঃ তরুবরঃ পুরতো ভাতি’—অর্থাৎ তরুদের মধ্যে বরণীয় এক নীরস তরু সম্মুখে বিভাসিত হচ্ছেন—এইখানে তিনি তরুতে মনুষ্যত্ব আরোপ করে সম্মানিত করলেন—ভাবকে প্রকাশের উত্তুঙ্গ মাত্রায় নিয়ে গেলেন। এইখানেই ভাল ও মন্দের কবিতার পার্থক্য।
‘কবিতার আলো’-র অভিমত
‘কবিতার আলো’-র মতে ‘সৌন্দর্যই কবিতার মূল গঠনবৈশিষ্ঠ্যের ধর্ম ও বক্তব্য’। কাব্যময় শব্দদ্যুতি পাঠকের মনকে বিভাসিত করে তোলে, ভাবকে তার অব্যর্থ লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে কবিতা স্থবির নয়, তার প্রকাশভঙ্গিও অটল অচল অপরিবর্তনীয় কোনও বস্তু নয়। আগেকার কবিতা আর এখনকার কবিতার অভিমুখ, ভাব আর প্রকাশ এক নয়। এটা আমাদের মানতেই হবে। কিন্তু তথাকথিত অনেক কবিই তা মানেন না, ফলে তাঁরা পুরনো কাব্যধাঁচেই পড়ে আছেন, যা এ যুগে শুধু বেমানানই নয়, হাস্যকরও কোনও কোনও ক্ষেত্রে। যুগ বদলাচ্ছে কিন্তু কবিতা বদলাবে না—এ তো হতে পারে না। তাই কবিতায় যুগযন্ত্রণার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী এবং তা অবশ্যই সাম্প্রতিক কবিতাভাষায়।
কবিতার ভাব ও প্রকাশ
সব ক্ষেত্রেই যেমন, কবিতার ক্ষেত্রেও তেমনই থাকে কালের দাবি। সেই দাবি মানতে হয়, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কালোত্তীর্ণ কবিরা তা মেনেছেন, তাই তাঁদের স্বকাল পেরিয়ে তাঁদের কবিতা আজও ভাস্বর। কিন্তু তাই বলে তাঁদের অনুসৃত ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি আজও অনুসরণযোগ্য—এ কথা সত্য নয়। সে যুগের ক্ষেত্রে তা যথাযথ থাকলেও এ যুগে তা অচল—এ কথা স্বীকার করার মধ্যে কোনও গ্লানি নেই।
যেমন তখনকার প্রাসঙ্গিক কিছু শব্দ বা শব্দবন্ধ এই যুগের কবিতায় অচল। যথা—‘তরে, মম, তব, নেহারি, অয়ি, লো, দিঠি, মোর পরে, ভ্রমি, উছলি, আজি, উচ্ছ্বসি, মোর, মোরে, দোঁহে, দুঁহুঁ, তেঁউ, তোরে, আমারে, তাহারে, কারে, কাহারে, যারে, যাহারে, বিসরি, পাশরি, জলকে, কী পরি, আজিকে, উথলি, মাঝে, সনে, সাথে, লাগি, স্মরি, জনমে, ত্যজি, নারি (পারি না অর্থে), হেরো, সিনান, অবগাহি, মরমে মরি, লভিনু, বরিনু, মাঝারে’ ইত্যাদি শব্দ বা শব্দবন্ধ আজকের যুগের কবিতায় ব্যবহার না করাই শ্রেয়।
একই কারণে ‘ডাবল ৭মী বিভক্তি’-ও পরিত্যাজ্য। ‘ঘরেতে, বনেতে, মনেতে, সাঁঝেতে, বসনেতে, সাগরেতে’ ইত্যাদি ডাবল-৭মী বিভক্তিযুক্ত শব্দ না ব্যবহার করাই ভাল। যেখানে ‘ঘর’ শব্দের ৭মীর একবচন ‘ঘরে’ বললেই মিটে যায়, সেখানে আবার ৭মী বিভক্তি ‘তে’ ব্যবহার করে ‘ঘরেতে’ করার কোনও যুক্তি নেই। তাই যুগের প্রয়োজনে এই সংশোধন। কিন্তু আজকের যুগেও বহু কবিই তাঁদের কবিতায় এই জাতীয় শব্দ অক্লেশে ব্যবহার করে চলেছেন। ফলে সেই কবিতাগুলি প্রকাশের দিক দিয়ে খারাপ কবিতা-র শ্রেণিতে গণ্য হচ্ছে। আমরা অগ্রসর হব সামনের দিকে—পিছনের দিকে নয়। অবশ্যই পিছন ফিরে তাকাব—সে আমাদের ঐতিহ্যময় অতুল রত্নভাণ্ডারের মণিমাণিক্যের আকর্ষণে—পথের দিশা নির্ধারণে।
ছন্দ-কবিতা/ পদ্যকবিতা
দুঃখের বিষয় অনেকেই ছন্দ না জেনেই ছন্দ-কবিতা বা পদ্য কবিতা লিখে থাকেন। তাঁদের কবিতায় পর্ববিন্যাস তথা মাত্রাবিন্যাস করা যায় না। প্রতিটি ছন্দের আলাদা নিয়ম ও চলন আছে। সেগুলি অনেকেই জানেন না বা জেনেও মানেন না। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে অন্ত্যমিলই বুঝি ছন্দ-কবিতা বা পদ্য কবিতার একমাত্র লক্ষণ বা পরিচয়। তাই তাঁরা ছন্দের চলনের তোয়াক্কা না করে যেমন-তেমনভাবে লিখে শেষে অন্ত্যমিল দিয়ে ভাবেন যে বুঝি সব দায় সারা হয়ে গেল। কিন্তু মনে রাখতে হবে অন্ত্যমিল ছন্দ নয়। তাই কবিতা লিখতে হলে (এমনকী গদ্যকবিতাও) আগে ছন্দ শিখতে হবে, তাদের চলন জানতে হবে, পর্ব/মাত্রাবিন্যাস জানতে হবে, তাল ও লয় জানতে হবে এবং বিভিন্ন ছন্দের পার্থক্যও জানতে হবে।
আবার অন্ত্যমিলেও হাস্যকর অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। যেমন—ভরা/তোড়া, গন্ধ/বন্ধু, চুপ ক’রে/ আর ঘরে, ঘাটে/লোটে, হোলি/তুলি, যাই/কেউ-ই, খেলা/(বালুকা)বেলা, বেড়ে/দূরে, ধরে/দূরে, আকৃতি/প্রশান্তি, ডালি/হোলি, লিখি/পাখি, বিনিদ্রা/তন্দ্রা, বাহানা/মাহিনা, ভাজা/মজা, শ্রেষ্ঠ/কষ্ট, যাই/কেউ-ই ইত্যাদি।
এখানে উল্লেখ যোগ্য যে একমাত্র শেষ অক্ষরের মিলই অন্ত্যমিলের মণিকাঞ্চনযোগ নয়। অন্তত শেষ দুটি অক্ষরের সাদৃশ্য ভদ্রগোছের অন্ত্যমিলের সহায়ক। এখানে ‘ভরা’-য় ‘ভ’ অকারযুক্ত, আর ‘তোড়া-য় ‘ত’ ওকারযুক্ত। ‘গন্ধ’-এ ‘ন্ধ’ অকারযুক্ত, ‘বন্ধু’-তে ‘ন্ধু’ উকারযুক্ত। ‘খেলা’-য় ‘খে’ ‘বিকৃত’ বা ‘অর্ধ-বিবৃত’ একার যুক্ত, উচ্চারণ ‘খ্যা’ আর ‘বেলা’-য় ‘বে’ ‘স্বাভাবিক’ বা ‘অর্ধ-সংবৃত’ একারযুক্ত, উচ্চার ‘বে’... ইত্যাদি। এইদিকে অবশ্যই দৃষ্টিপাত আবশ্যক।
গদ্যকবিতা
মনে রাখতে হবে যে যুগের প্রয়োজনেই গদ্যকবিতার জন্ম হয়েছে। কিন্তু ছন্দের মধ্যে থেকেই ছন্দ ভেঙেই তার জন্ম। এই জন্ম হয়েছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মুক্তক থেকে—তা আবার দুই প্রকার—ক) সমিল মুক্তক ও খ) অমিল মুক্তক। মুক্তক-এর অর্থ-- সব পঙক্তিতে সমমাত্রার পর্ব থাকে না। কোনও পঙক্তিতে হয়তো ‘৮—৬—২’ মাত্রার পর্ব। আবার কোনও পঙক্তিতে ‘৬—৪—২’ মাত্রার পর্ব।
সমিল মুক্তকে অন্ত্যমিল থাকে কিন্তু অমিল মুক্তকে অন্ত্যমিল থাকে না। এই মুক্তক থেকেই গদ্যকবিতার জয়যাত্রা শুরু। সেখানে এইসব পর্ব বা মাত্রার বিষয়টি সেভাবে না থাকলেও একটা অন্তর্নিহিত ছন্দের দোলা থাকেই। তাতেই কবিতা প্রাণস্পর্শী হয়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অনেক গদ্যকবিতায় সেই ছন্দের অন্তর্লীন দোলাটুকু অনুপস্থিত থাকে। তাই তা নিষ্প্রাণ শব্দগুচ্ছ ব্যতীত আর কিছুই নয়—কবিতা তো নয়ই, খারাপ কবিতাও নয়।
কবিতার ভাল-মন্দ
ভাল কবিতা তখনই হয় যখন তার ভাব ও প্রকাশ দুই-ই ভাল হয়। কেবল ভাব ভাল—কিন্তু প্রকাশ তদনুরূপ নয়, সেক্ষেত্রে সেটি ভাল কবিতা হতে পারে না। আবার ভাব ভাল নয়, কিন্তু প্রকাশ খুব ভাল—সেক্ষেত্রেও তা ভাল কবিতা বলে বিবেচিত হবে না।
একটি সার্থক গদ্যকবিতার উদাহরণ—
ছায়া
শ্রী কৌশিক দাস
“সে আমাকে একটি গাছের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে চলে
গিয়েছিল একদিন।
গাছ নেই, কেবল ছায়াটি আঁকড়ে আমি পড়েছিলাম নিযুত বছর।
একদিন বিকেলবেলা ছায়াটি ছাই রঙা পাখি হয়ে উড়ে যেতে
যেতে বলে গেল—
“প্রেমিক, বাড়ি যাও! ছায়ারা চিরদিন পলাতক।”
দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরি! দরজা অবধি অনার্য ঘাস। কেবল তুলসী
তলায় আমলকি গাছের নীচে একটি ন্যূব্জ ছায়া মুছে যেতে যেতে
বলে গেল—
“খোকা, এত দেরি করলি!” (‘কবিতার আলো’-য় প্রকাশিত)
এখানে ছায়ার প্রতীকের আড়ালে এক অমোঘ সত্যকে কত রঙে এঁকে দিলেন কবি। আমাদের মনও ছায়ামেদুর হয়ে ওঠে অনায়াসে।
উগ্র আধুনিকতার নামে উগ্র যৌনসর্বস্বতা
অতি আধুনিকতামনস্ক কিছু কিছু কবি ভাবেন উগ্র যৌনসর্বস্বতাই বুঝি ভাল কবিতার একমাত্র বৈশিষ্ঠ্য। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে তা আমাদের দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সুসমঞ্জস নয়—কাব্যসরস্বতীর সঙ্গে তো নয়ই। কবিতার পঙক্তিতে পঙক্তিতে যৌনতার উদগ্র নিদর্শন—এতে তাঁদের যৌন প্রদর্শনবাতিকের স্ফুর্তি হয় বটে কিন্তু কাব্যসরস্বতীর আত্মিক অস্বস্তি বাড়ে বই কমে না। অথচ উগ্র যৌনতার প্রদর্শন না করেও মানব-মানবীর প্রেম সুস্নিগ্ধভাবে বর্ণনা করা যায়। আমি সেই অর্থে কবি নই, তবু আমার একটি কবিতায় বিনম্রভাবে তা দেখাতে চেষ্টা করেছি—
‘চুম্বন-ক্ষণ’
কোথায় ছিল তোমার দীপ্র সাহস-ভরা মন?
নাওনি কেন এতদিনেও একটিও চুম্বন?
বিষের ভয়ে? কোলাহলের উদগ্র দর্শন
কেড়েই নিল এ দুজনার অলীক কিছু ক্ষণ?
আর কি এসে সেই পাখিটা তাকাবে জুল জুল!
আর কি ঝুঁকে পড়বে ঝরে কুমারী বকুল!
ভেসে যাওয়া প্রতি নিমেষ ছিল সমুৎসুক,
বৃথাই দিলে বেচারীদের অভাবিত দুখ।
হত না হয় একটি নিমেষ অজর চিরন্তন,
হত না হয় কালের বুকে ছায়াপথের ধন।
বাইরে না থাক, ও বসন্তের এবুকে অবস্থান,
অন্তত চুম্বনে তাকেও এইটুকু দাও মান।
টলুক গিরি, উঠুক ঝঞ্ঝা, প্রবল জলোচ্ছ্বাস,
একঘেয়েমির আঁস্তাকুড়েও আসুক না বিভাস।
নব যুগের কবি লিখুন ‘গীতগোবিন্দম্’,
নতুন রবি বর্মা আঁকুন আভাস মনোরম।
এটি ভাল না মন্দ কবিতার মধ্যে পড়ে, সে বিচারের ভার আপনাদের উপরই ছেড়ে দিলাম।
পুরাতন প্রকরণে ভাব ও প্রকাশের আধুনিকীকরণ
পুরাতন রীতিকে যুগোপযোগী করে নতুন ভাবের বৈভবে রসস্থ করেও অনায়াসে প্রকাশ করা যায়। তাতে অতীত বর্তমানের দ্বারে এসে সুরম্য হয়ে ধরা দেয়। যেমন—বিশিষ্ট কবি ও ‘কবিতার আলো’-র সম্পাদক শ্রী বৈজয়ন্ত রাহা মহোদয়ের রচিত নীচের সনেটটি—
স্বপ্ন
যেভাবে অধর তোলে বিষাদের আলো
প্রেমিকার দেশ থেকে উৎসের খোঁজে
জলের মিনার জানে সেভাবে ঘনালো
নদীর ভিতরে নদী, ভুলে চোখ বোজে,
অকারণে দূর চায় নিকটের দূর,
সাঁজবেলা লুফে নেয় রাতচোরা স্তব
হেরে যাওয়া বাঁশি শোনে রাখালিয়া সুর
ঘরে ঘরে ঘোরে নদী, মরা উৎসব
জল তাই চুপ চাপ নীচে বয়ে যায়
শিয়রে বসেনি আলো, ঘুম স্মৃতিহীন
কাছের মানুষ শোনে সাঁকো-বাহানায়
নদীর উপর নদী ভেসে থাকে ক্ষীণ
চিবুকে আঙুল রাখি, চোখে রাখি চোখ
আজ থেকে সব কষ্ট শুধু আমি হোক
আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না কী ভাবে অধুনা প্রায় অব্যবহৃত একটি প্রকরণে ভাষা মাটির কাছাকাছি এসে বুকে নাড়া দিয়ে গেল “আজ থেকে সব কষ্ট শুধু আমি হোক”—এটি সত্যিই ভাবে ও প্রকাশে একটি ভাল কবিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।
ভাল কবিতা নিয়ে কিছু কথা
শ্রী রাহার মতে কবির মননের স্তরই কবিতায় ফুটে ওঠে। ভাল কবিতা এক এক বার পড়লে এক এক রকম ভাব ফুটে ওঠে।
কবির হৃদয়ে কল্পনা এবং কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তশক্তির সহাবস্থান। কোনও কিছুর সঙ্গে আত্মিক সংযোগ-স্থাপনই হল ভাল কবিতার জন্মের উৎস। পথের পাশে একটি বুনোফুল পড়ে আছে। কেউ তা লক্ষ করেন কেউ বা করেন না। যিনি ওই বুনোফুলের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ স্থাপন করতে পারেন এবং তাঁর কবিতায় তাকে অনুভবের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত কবি। আর প্রকৃত কবি ক্ষণজন্মা প্রাণ।
ভাল কবিতা পড়লে বা শুনলে মন আনন্দে রিন রিন করে বেজে ওঠে, তার প্রভাব অনেক দিন পরেও রয়ে যায়। কবির যন্ত্রণা কবিতার আঁতুড়ঘর। কবি তাঁর যন্ত্রণাকে আস্বাদ্যমান এবং রসময় করে কবিতায় প্রকাশ করেন। ব্যক্তিগত আনন্দকেও আস্বাদ্যমান ও রসময় করে সার্বজনীন করে প্রকাশ করেন। বেদনার অনুভূতিকে দ্রষ্টা হয়ে বিশ্বজনীন করে তোলেন।
কবির অলৌকিক ক্ষমতা আছে, শব্দ দিয়ে অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারেন। কবি শুধু কবি নন। কবি দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, অদ্ভুত মনের অধিকারী। কবি আল মাহমুদ বলেছেন যে কবি পারেন নিজের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, উপলব্ধি ও অনুভবগুলিকে সীমানা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে।
আমাদের মনে রাখতে হবে যে কবির নিজের মনে নিজস্ব সাম্রাজ্য আছে। এর সঙ্গে বাস্তবজগতের সত্যের কোনও মিল নেই। তাই কবিতার সঙ্গে বাস্তবজগতের মিল খুঁজতে গেলে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। কবির বয়স হয় না। কবিতায় কবিকে চেনা যায়। কবিতা যখন প্রকৃত অর্থে কবিতা হয়ে ওঠে, তখন আর ভাল কবিতা ও খারাপ কবিতা বলে কিছু থাকে না। কবিতা তখন সব কিছুর ঊর্ধ্বে ভাস্বর ও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।
উপসংহার
প্রকৃত ভাল কবিতা লিখতে গেলে আগে আত্মস্থ হতে হবে, ভাবের অনুভবে মনকে ঋদ্ধ করে প্রকাশের যুগোপযোগী দিশা খুঁজে নিতে হবে। তবেই রসময় সুন্দরের আবির্ভাব হবে—অক্ষরে অক্ষরে তার রসঘন অবস্থান ঘটবে। এটি সারস্বত সাধনার পৌনঃপুনিক অনুশীলনের ফলেই সম্ভবপর হবে।
কথাচিত্র
নির্বিকল্প - দ্বিতীয় অঙ্ক
মনি ফকির
আহা, চা টা বড্ড ভালো বানিয়েছ। অনেকদিন পর।
এভাবেই থেকে যাবে? পাল্টাবে না?
না। এভাবেই। বদলে যাওয়াটা খুব কষ্টকর। আমার অভিযোজন পোষায় না।
কিন্তু, তুমি কেন এভাবে আটকে গেলে। আমাদের তো কথা হয়েছিল, কেউ কাউকে আটকাবো না।
আমায় তো তুমি আটকাও নি।
কিন্তু তুমি আমায় আটকে দিয়েছ। আমি মুক্ত থাকতে চাই।
এই শোনো না। এতদিন পর এসেছ, এসব কাটাও। একটা কথা বল।
কি?
হঠাৎ এত দিন পর এলে। কেন?
সব কারণ তোমায় জানতে হবে?
একদম নয়। নিছক কৌতূহল।
বলব না। আমার এসব ভালো লাগছেনা। আমি আসি।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।
কি হলো হাসছ কেন?
যেতে চাইছো, অথচ আসি বলছ। আর এদিকে আমায় হেবি ফান্ডা দিলে, মুক্তি, চুক্তি কত কি।
খুব মজা লাগছে তাই না?
দারুন। এই শোনো তুমি রূপকথায় বিশ্বাস কর?
না।
আর পরী? পরী মানো?
কি আজগুবি কথা বল না। আর একদম অপ্রাসঙ্গিক।
আরে সত্যি বলছি, সব মানুষের একটা একান্ত ব্যক্তিগত রূপকথা থাকে। আর পরীও। অবশ্য তাদের ডানা থাকেনা, আর গোলাপী ফুল ফুল গাউন পড়ে, হাতে জাদু ছড়ি নিয়েও ওড়ে না।
মানে ডানাকাটা পরী?
একদম।
তা যদি থেকেই থাকে, তাতে কি।
কিছুই না। কেউ মানতে চায়না। বা বিশ্বাস করেনা। আমি সেই বিশ্বাস টি ফেরৎ আনতে চাই।
এনে কোন মোক্ষ লাভ হবে শুনি?
আরে মানুষের অপরাধ প্রবণতা অনেক কমে যাবে। তুমি দেখ।
তোমার সাথে ওর যোগাযোগ নেই।
আছে।
আসে না?
আসবে, ও একদিন আসবে। এখানে কিছু ফেলে গেছে।
ওহ্। কি ফেলে গেছে?
তা তো জানি না। কিন্তু কিছু একটা ফেলে গেছে। এই তুমি নিয়ে যাও না।
পাগল নাকি। আর কারো জিনিস, আমি কেন নেব?
আরে নিয়ে যাওনা। আমার তো নিজের ই ঠিক নেই।
আর সে এসে যদি খোঁজে; তখন?
তোমার ফেলে যাওয়া জিনিস টা দিয়ে দেব ওকে। আবার কি।
হাহা, তুমি না যা তা। আচ্ছা তোমার জানতে ইচ্ছে করে না?
কি বলত?
আমার কথা। আমি কি করছি, কেমন আছি?
না। কারণ আমি জানি সব। আর তুমি এখন কি করছ, তার জেনে আমার কি।
সেদিন নন্দনে, তোমার আমাকে ওর সাথে দেখে, খারাপ লাগেনি?
না।
হিংসে হয়নি?
এক ফোঁটা ও না।
বাজে কথা। একদম মিথ্যে কথা।
না। যা আমার কখনোই ছিল না, তা নিয়ে আমার অধিকার বোধ নেই।
আরে অদ্ভুত ব্যাপার। তোমার একটাও ইন্সট্রুমেন্ট দেখছি না!
দিয়ে দিয়েছি। একটা হোম এর বাচ্চাদের।
সেকি কেন?
ওরা বাজাক না। আমার এখন আর দরকার নেই।
আর লেখা গুলো?
সব পুড়িয়ে দিয়েছি।
তুমি কি পাগল নাকি? কেন এসব করছ।
শোনো, আমার গান, কথা, সুর, সৃজনশীলতা - আমার ওপর বড্ড ছড়ি ঘোড়াচ্ছিল। আমার পোষায় না। আমি কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারবোনা। আচ্ছা একটা উপকার করবে?
বল।
গাড়ি এনেছ?
আমায় একটু নামিয়ে দেবে।
কোথায়?
যেখানে ইচ্ছে। আমি নিজেই যেতাম কিন্তু, একটু লোভ হলো, তুমি এগিয়ে দাও।
এই অসুস্থ শরীরে কোথায় যেতে চাও।
শরীরের আবার কি। জীর্ণ হলে, খোলস পাল্টে নিলেই হবে। আমি কোথায় যাবো ঠিক করিনি, তবে এমন কোথাও যেখানে আবার শূণ্য থেকে শুরু করব।
কোনো যোগাযোগ থাকবে না?
না। তবে আবার দেখা হবে। আবার নতুন করে বন্ধুত্ব হবে। আমার লাস্ট অ্যাটাচমেন্ট এই লেখার খাতা টা নিয়ে যেও। তোমার জন্যই রাখা ছিল।
মুক্তপদ্য
গোল্ডেন ড্রপ
নীলম সামন্ত
এবং একটা ঈশ্বরহীনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঘুম পায়। প্রচন্ড ঘুম। আমাদের বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত এমন কোন ব্ল্যাকহোল পায়নি যার ভেতর ভগ্নপ্রায় মানুষরা পিঠ ঠেকিয়ে একটু জিরোতে পারবে৷ তাই নক্ষত্ররা জিরিয়ে নেয় দুদন্ড। নক্ষত্ররা জিরোতে বসে হাতে করে মেঘ নামিয়ে আনে। জমা করে শাঁখের ভেতর৷ খুব ছোটবেলায় শুনেছিলাম শাঁখের ভেতর ঘুমিয়ে ছিল বাড়ির বাস্তুসাপ৷ আমার ভেতর কে যে ঘুমিয়ে আছে দীর্ঘদিন।
কেউ ঘুমোলেই আমি ঘুমোতে পারি তা নয়৷ রাত বাড়লে বালিশে কান পেতে শুনি জলডুবি হওয়া ছেলেটির গোঙানি। অথচ যখন গ্রামের বাড়ি যাই ঈশ্বর চেপে থাকতেন। যিনি আমার ঈশ্বর তাঁর পায়ের ছাপে একবার জন্মেছিল একশ আটটা প্রজাপতি৷ আমি শাঁখ বাজিয়েছিলাম। শাঁখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল নদী৷ যার নাম এখন আর মনে নেই৷ তবে আমার ঈশ্বরের ব্যক্তিগত কোন নদী নেই৷ পাখি আছে৷ খাঁচায় আটকানো দিন রাত৷ নাম জানিনা। আমি যা জানি তা খুবই সহজ সরল। ঈশ্বর ও তার নরম পা।
একদিন দুপুরে ঈশ্বরের পা ছুঁয়ে বন্ধুকে বলেছিলাম "দেখ কী নরম"! উত্তরে বন্ধু হেসেছিল। বলেছিল " ভঙ্গুর"। পায়ের পাতায় হাত বুলিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম গাছের শেকড়ে কতখানি জল, কতখানি মাটি। তিনি পা সরিয়ে নেননি। শিরা উপশিরা ছড়িয়ে আঁকড়ে ধরছিলেন আবেশ৷ সেদিন ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করা হয়নি ওনার ব্যক্তিগত কোন গাছ আছে কিনা। গাছেদের কি গাছ থাকে? হয়তো থাকে, হয়তো বা না৷ কেউ কেউ তো নিজেরাই নিজের ছাদ-ছাতা।
আমাদের দেখা হয়নি বহুকাল। কিছু মুহুর্ত ভুলতে নেই বলে মনে করি। মনে করতে করতে দেখি ঈশ্বর গাছ শাঁখ নদী সাপ সকলেই হাসছে ছবির মত। খাঁচার পাখি তার উলম্ব প্রতিবিম্বে লিখে রাখছে করতালি ও অন্ধকারের সমীকরণ। উপসংহারে বার বার লিখছে হাতে হাত মিললে অন্ধকার জন্মায়। সে করতালিই হোক বা করমর্দন৷ আচ্ছা, এক কথা বার বার লিখলে কি খুব বেশি ঝংকার তৈরি হয়? হয়তো হয়৷ আমার জানা নেই। আমার জানা নেই কারণ আমি লিখতে পারি না৷ যেটুকু কথা বলি তা জলের সাথে। যখন শরীর থেকে নদী বেরিয়ে যায় তখন গ্লাসে করে জল খাই৷ সব শেষে হাতের ওপর রেখে দিই গোল্ডেন ড্রপ৷
ঈশ্বর বলেন আমি গঙ্গার মত শান্ত, গঙ্গার মতই উত্তাল। ভরা কোটালের দিন আমার গায়ের রঙ গোলাপি হয়ে যায়৷ আর ভাটার সময় মাটি। আমি কি নদী? তিনি জানেন। তিনি সব জানেন। তবে খোল করতাল খঞ্জনির উল্লাস জন্মাইনি একবারও৷ সেকথা সে বলেনি৷ বলেনি বলেই আজও অপেক্ষা করি মুক্ত আকাশে নবজন্মের ; মেঘের নদী কিংবা গাছ গাছালির ফলদায়ী মা।
অরাজনৈতিক ভ্রম
রাজনীতি আসলে এক জমি
কৌশিক চক্রবর্ত্তী
অরাজনৈতিক শব্দটি কতটা যৌক্তিক? সব সিদ্ধান্তের পিছনে থাকে কোনো না কোনো অরাজনৈতিক ভ্রম। "আমি নিরপেক্ষ" এই শব্দবন্ধের প্রতিবন্ধকতা অনেক। আসলে আমরা নিঃশব্দে হেঁটে গেলে পায়ের শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু আমরা হাঁটছি না সে কথা কতদূর প্রাসঙ্গিক? আপনি কোন সিদ্ধান্তকে রাজনীতির বাইরে রাখছেন? রাজনীতি অর্থে কী? রাজার নীতি? কদাপি না। রাজা শব্দটি বড় আপেক্ষিক। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে"। অর্থাৎ রাজ মনন অন্তরে। মুকুট পরলেই রাজা হওয়া যায় না। রাজা সন্ন্যাসীও হতে পারেন। আবার কপর্দকশূণ্য হাতে রাজা বনবাসীও হতে পারেন। আমরা জানি রাজা হরিশ্চন্দ্র ডোমের জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। সেই অর্থে দেখতে গেলে আপনার রাজত্ব আপনার অধীনস্থ। আর সেই রাজত্বে সব সিদ্ধান্তই রাজনৈতিক।
এই ধরুন বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনকে ধরা যাক। সংরক্ষণ আইনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আজ ঢাকা, ময়মনসিংহ, বড়িশাল বা কুমিল্লার পথে পথে আগুনের লেলিহান সর্বগ্রাসী শিখার মত ছড়িয়ে যাচ্ছে, তা একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আর একটি রাজনৈতিক লড়াই। ঝাণ্ডা রাজনীতির পরিচয়৷ তবে দেশের পতাকা হাতে রাজপথে দাঁড়িয়ে থাকা যুবক কিভাবে নিজেকে অরাজনৈতিক ব্যক্তিসত্তায় পরিচয় করাতে পারে? রাজনীতি এক মঞ্চ। যে মঞ্চের মধ্যিখানে আমরা সবাই দক্ষ বা অদক্ষ কুশীলব। সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনার সন্তান চিন্তা করছে কিভাবে স্কুলে পৌঁছে সম্পূর্ণ না হওয়া হোম ওয়ার্কের খাতা জমা দেবার হাত থেকে বাঁচতে হবে। একবার ভাবুন তো। এরমধ্যে কি রাজনীতির কোনো পাঠই নেই? আসলে রাজনীতি আমাদের আত্মায়। প্রতিদিন আমরা এক অরাজনৈতিক ভ্রমের আবহে বাস করি৷ অরাজনৈতিক শব্দটাই এক অবাস্তব বিভ্রম। সামাজিক পরিকাঠামোয় এর কোনো অস্তিত্ব নেই। অরাজনৈতিক সত্তা নেহাতই এক আস্ফালন। আর এই আস্ফালনের মধ্যে থাকে এক মোড়কের আস্তরণ। তার ভেতরে আমরা স্বচ্ছন্দে বাস করবার চেষ্টা চালাই৷ অথচ নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বটুকু লুকিয়ে সমাজে নিজস্বতার মিথ্যে জাহির করে বেড়াই সাবলীল ভাবে৷
বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ছাত্র আন্দোলন বর্তমান সময়ে সব থেকে বড় রাজনৈতিক ইস্যু৷ দেশে সংরক্ষণ আইনের বিরুদ্ধে পথে নামে ছাত্রদল। কী তাদের রাজনৈতিক সত্তা? তারা ছাত্র। দল বিচার করলে তারা ছাত্রলীগ হতে পারে। কিন্তু এই লীগের বাইরে তাদের সবথেকে বড় পরিচয় তাদের ছাত্রসত্তা। আর ছাত্রাবস্থায় যে রাজনৈতিক পাঠ মস্তিষ্কের দখল নেওয়া শুরু করে, সেই মতাদর্শই সারাজীবন পরিচালিত করে আপামর জীবনের স্রোতকে। তাই ছাত্রাবস্থা হল রাজনীতির হাতেখড়ির সময়৷ কিন্তু সেই সময় যদি কোনো ছাত্রকে প্রাণ দিয়ে তার দাম দিতে হয়, তবে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক কিছু হয় না৷ ১৯৫২ থেকে ২০২৪। মাঝের এই সময়টায় অনেক বদলেছে ঢাকা। কিন্তু বদলায়নি ছাত্রদের রাজনৈতিক সত্তা৷ যে বল বুকে নিয়ে বরকতরা ছাত্র রাজনীতির পতাকা বহন করে পথ এটা ছিল ঢাকার রাজপথে, এই ক্ষেত্রে দলই আবু সাঈদের বেশে রাজনৈতিক সত্তাটুকু বাঁচিয়ে রাজপথে বুক চিতিয়ে গুলি খেল। এবং সেই রাজনৈতিক সত্তার ক্ষমতাটুকুর বলে হয়ে গেলে গুলি খাওয়ার পরেও দাঁড়িয়ে থাকে হাজার মানুষের মধ্যিখানে। রাজনীতি আসলে এক জমি৷ যে জমির উপর দাঁড়িয়ে মানুষ কথা বলতে পারে, যে জমির উপর দাঁড়িয়ে মানুষ হিসাব চাইতে পারি। আর ব্যক্তি সত্তায় এই হিসাবটুকু চেয়ে নেওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক সত্তা বুকে নিয়ে শহীদ হবার ঘটনা আজ প্রথম নয়। ক্ষুদিরাম বসু যদি এই প্রথার পুরোধা ব্যক্তিত্ব হন, তবে তার রাজনৈতিক সত্তার অহংকারই তার শহীদ হওয়ার শক্তি। রাজনীতি জীবনকে নাড়া দেয়৷ একটি ভোট একটি গণতান্ত্রিক মতপ্রকাশের মঞ্চ৷ আর সেই ভোটের আড়ালে মিশে থাকা মনন আকাশচুম্বী। সেখানে অনেক লড়াই, অনেক আন্দোলন।
প্রতিটি মানুষের জন্য সবার প্রথমে দরকার মঞ্চ। সে সাংসারিক পরিমণ্ডলেই হোক, বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা কর্মক্ষেত্রে৷ রাজনৈতিক মঞ্চ বেঁধেই আমরা হেঁটে যাই প্রতিটা দিন। রোজকার লড়াইয়ে স্বীকৃতির জায়গাটাই তো রাজনীতির সহজ পাঠ।
ডাকঘর
আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম
পার্থ মুখোপাধ্যায়
প্রিয়মুখ,
"আজ বিকালের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম"। এই চিঠির অপেক্ষায় আজ আর কেউ থাকেনা। অতীতে চিঠি লেখার পর প্রত্যুত্তরের জন্য দরজায় অপেক্ষা করত পরিজনেরা। এটা ছিল খুব স্বাভাবিক। যুগ বদলেছে। আমরা বদলেছি। "একটা মেসেজ করে দিও" এখন এটি একটি সাধারণ কথা। তবুও চিঠি লেখার অতীত নিয়ে কখনোও কখনোও মনে হয় এসব কথা। তাই ইচ্ছে হল আজ তোমাকে চিঠির নস্টালজিয়ায় ভিজিয়ে দিই। মূল স্রোতে ফেরা যাক। জানো, কবিগুরু তাঁর জীবনে প্রায় সাড়ে সাত হাজার চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর লেখা সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে চিঠি বোধহয় কিছু কম হবেনা। একথা স্বয়ং তিনি জানিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন কে। তাঁর চিঠির ধারা বিভিন্ন জনের জন্য ছিল বিভিন্ন রকম। তবে নারীদের কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলো যেন একটু বেশিই পক্ষপাত দুষ্ট। কবি অমিয় চক্রবর্তীর মা অনিন্দিতা দেবীকে লেখা চিঠির মধ্যে কবিগুরু বলেছিলেন "মেয়েদের দুঃখ ও অবমাননায় চিরদিন আমি দুঃখ ও বেদনাবোধ করি"।
পত্নী মৃণালিনী দেবীকে প্রায় ৩৬ টির মতো চিঠি তিনি লিখেছিলেন। ইতিউতি চিঠি আরোও দুই একটি পাওয়া গেলেও প্রত্যুত্তরে সাতটির বেশি চিঠি পাননি। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনুযোগ, "বড় হোক, ছোট হোক, ভালো হোক, মন্দ হোক, একখানা করে চিঠি আমাকে রোজ লেখ না কেন, ডাকের সময় চিঠি না পেলে ভারী খালি ঠেকে।" তাঁর দুই কন্যা বেলা ও মীরাকেও কবি চিঠি লিখেছিলেন। জ্যেষ্ঠা বেলাকে পাঁচটির মতো চিঠি লিখেছিলেন, অপরদিকে কনিষ্ঠা মীরা দেবীকে লিখেছিলেন ৮১টির মত চিঠি। এর মধ্যে সবচাইতে মর্মস্পর্শী চিঠিটি লিখেছিলেন মীরার একমাত্র পুত্র নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে।
"শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্চে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি— সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্য আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে।" পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর একথা লিখেছিলেন কবিগুরু।
পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে ১১৫ টি চিঠি লিখেছিলেন। ইন্দিরা দেবীকে (তার ভ্রাতুষ্পুত্রী) লেখা চিঠি গুলি 'ছিন্নপত্র' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই চিঠি প্রকাশের জন্য কবিগুরু তাঁর সম্মতিও নিয়েছিলেন। নির্মলা কুমারী মহলানবীশ কে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক চিঠি লিখেছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নির্মলা কুমারী মহলানবীশ কবিগুরুর মৃত্যুরদিন পর্যন্ত তাঁর পাশেই ছিলেন। লেডি রানী মুখার্জিকে লেখা ৫৯টি চিঠি সংকলন যা 'ভানু সিংহের পত্রাবলী' নামেই খ্যাত। অবশ্য সব মিলিয়ে ২০৮ টি চিঠির আদান প্রদান লেডি রানু মুখার্জির সঙ্গে হয়েছিল।
আসলে এই চিঠির আদান-প্রদানের বহু সূত্র মৃত্যুর পরও দলিল হিসেবে রয়ে যায়। বর্তমানে চিঠির গুরুত্ব কমলেও ব্যক্তিগত স্তরের মেসেজের আদান-প্রদান কখনোও সাধারণ, কখনোও রাজনৈতিক কখনোও বা একান্ত ব্যক্তিগত। সবই রয়ে যায়। হাতে লেখা চিঠির সঙ্গে তুলনা করলে এর রূপ বদল হলেও "জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে "-- এই বার্তাগুলিরও কখনোও কখনোও ঐতিহাসিক মূল্য থেকে যায় বৈকি। অসুস্থ অবস্থায় কিছু চিঠি কবিগুরু নিজে হাতে লেখেননি। তাতে চিঠির গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে না। বর্তমানের বার্তা আদান-প্রদানের জগতেও এমন বহু তথ্য থেকে যায় তা প্রামাণ্য এবং অন্যের কাছে সুরক্ষিত থাকে। যাকে বলা যেতে পারে #Golden Treasury...
যাকগে অনেক কথা লিখে ফেললাম। আসলে এই কথাগুলো তোমার সঙ্গে চিঠি লিখেই ভাগ করে নিতে ইচ্ছে হল। এর উত্তরও এমন আকাশ রঙা ইনল্যান্ডেই চাই কিন্তু।
ভালো থেকো, ভালো রেখো।।
ইতি
পার্থ মুখোপাধ্যায়
ডাকঘর
মাদ্রীর চিঠি
অদিতি সেনগুপ্ত
মহাভারতের একটি অবহেলিত চরিত্র মাদ্রী। তাঁর অব্যক্ত কথনকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করলাম কুন্তীকে লেখা তাঁর এই চিঠির মাধ্যমে।
দিদি,
এই চিঠি যখন আপনার হাতে এসে পৌঁছবে তখন আমার নশ্বর শরীরটা পুড়ে একমুঠো ছাই হয়ে গেছে! অন্তরে কিছু কথা জমে পাহাড় হয়ে আছে বহুকাল যাবত। সেগুলি সঙ্গে নিয়ে যদি চলে যাই তাহলে আমার আত্মার মুক্তি ঘটবে না। তাই এই চিঠি রেখে গেলাম। স্বামীর চিতায় সহমৃতা হওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ আমার। জীবনে অন্তত এই একটা বিষয়েই হয়তো আমার ইচ্ছে গুরুত্ব পেলো। আসলে আপনার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ মন থেকে মেনে নিতে পারেননি ভীষ্ম, কারণ আপনি ছিলেন বেদব্যাসের পছন্দ। আর গোড়া থেকেই ব্যাসদেব এবং ভীষ্মের অন্তর্দন্ধ সর্বজনবিদিত। এরই ফলস্বরূপ আপনার স্বামী আমারও স্বামী হল! মদ্রদেশের নিয়ম অনুসারে কন্যাপণ দিয়ে আমাকে একপ্রকার কিনেই নিলেন মহান ভীষ্ম। মদ্ররাজ শল্যের সাহসও ছিল না তাঁর এই প্রস্তাবের অন্যথা করার। কারণ তাঁর স্মরণে ছিল কাশীরাজকন্যাদের বিবাহবিভ্রাট। যাই হোক বিবাহ সুসম্পন্ন হল এবং অষ্টাদশী আমি এলাম কুরু বংশের বধুরূপে। যদিও আমার অন্তর জানত যে, এ বিবাহ কখনই সুখকর হবে না। কেননা কোনো নারীই তার স্বামীর অধিকারের বিভাজন মেনে নিতে পারে না। আমার এই বৈবাহিক অসুখের মূল হোতা ছিলেন ভীষ্ম, ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছি কুরু বংশের রাজা না হয়েও যাবতীয় ক্ষমতা ছিল তাঁরই কুক্ষীগত। আসলে রাজপরিবার গুলোতে রাজকন্যাদের সঙ্গে এমনটাই হয়ে থাকে! গান্ধার রাজকন্যাও ছিলেন এর শিকার। নিজেদের অহং সন্তুষ্ট চরিতার্থ করতে আমাকে বেচাকেনার এক সামগ্রীতে পর্যভূষিত করা হল। কোনো আত্মসচেতন নারীই কী এটা মেনে নিতে পারে আপনিই বলুন! তবে হ্যাঁ... এ বিবাহ কূটনৈতিক চালের ফলাফল হলেও একথা অস্বীকার করব না যে আমি মহারাজকে অন্তর থেকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম!কেননা স্বামী হিসেবে তিনি ছিলেন উদার। এক প্রকৃত বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছিলাম আমি তাঁর মধ্যে। হয়তো শারীরিক সুখ দিতে না পারার অপারগতায় মনকেই সুখের আধার করে তুলেছিলেন তিনি। আর নারীর মনকে যে পুরুষ আশ্রয় দিতে পারে তাকেই ভালোবেসে ডুবে যায় নারী। ভেবে নিয়েছিলাম নাই বা হলো যৌন মিলন, স্পর্শসুখই বা কম কী? ভেদন নয়, প্রবল আশ্লেষের একটা চুম্বনও সুখের শীর্ষে পৌঁছে দিতে পারে। আমরাও তেমনই শারীরিক লিপ্সার আগ্রাসী খিদেকে নিষ্কাম ভালোবাসার উন্মুক্ত জমিতে মুক্তি দিয়েছিলাম।
কিন্তু এবং কিন্তু, আপনার যে অন্য ছক ছিল আর্যপুত্রকে নিয়ে! আর এই ছককে বাস্তবায়িত করতে উনিই ছিলেন আপনার একমাত্র অস্ত্র। নিজের জাগতিক বাসনাকে চরিতার্থ করতে কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হননি আপনি। আবার ভাগ্য প্রতিকূল থাকলেও রাজমাতা হবার প্রবল ইচ্ছেকেও ত্যাগ করেননি কখনও। তবে একথাও ঠিক যে আপনার মধ্যে রাজমাতা হবার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। আসলে ভীষ্মের পরে কুরুবংশে বহিরাগত রক্তের প্রবেশ ঘটল। কেউই আর বিশুদ্ধ কৌরব রইল না। ধৃতরাষ্ট্র এবং আর্যপুত্র দুজনেই ছিলেন ব্যাসদেবের ঔরসজাত। কিন্তু অন্ধত্ব ওনার জ্যেষ্ঠপুত্রর থেকে সিংহাসন কেড়ে নিল। এখন যদি ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান জ্যেষ্ঠ হয় তাহলেই সে রাজা হবে। এই আশংকা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে দিচ্ছিল না ওঁদের জৈবিক পিতাকে। কিন্তু কেন! দুজনেই তো ওনার সন্তান! তাহলে উনি কেন চেয়েছিলেন পাণ্ডুপুত্রই সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করুক! আসলে এর নেপথ্যেও ছিল সেই গভীর অহং যুদ্ধ। যেহেতু ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের ক্ষেত্রে খাটেনি ব্যাসের কূটনীতি, তাই আর্যপুত্রের বিয়ে দিয়েছিলেন উনি নিজের পছন্দে। কিন্তু আর্যপুত্রের শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও উনি এই বিবাহ সংঘটিত করেছিলেন কেন? আসলে তিনি জানতেন দুর্বাশা মুনির থেকে প্রাপ্ত আপনার সেই বরের কথা, যে বরের জোরে চাইলেই আপনি হয়ে উঠতে পারেন দেবভোগ্যা এবং লাভ করতে পারেন তাঁদের ঔরসেজাত সন্তান।
আপনিই তো রাজি করিয়েছিলেন আর্যপুত্রকে ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্য। মনে পড়ে আপনি তাঁকে বলেছিলেন, "এ পরিবারের এ রীতি নতুন কিছু তো নয়! মনে রেখো জীবনে জয়লাভ করাটাই মূখ্য, জয় কোনপথে এলো সেটা কেউ মনে রাখেনা, মনে রাখে জয়ীকে।" আপনার মানসিক দৃঢ়তা যে সাংঘাতিক তাতো বলাই বাহুল্য। তাইতো আপনি রাজপরিবারে থেকেও স্বামীর বর্তমানে আমাদের দেবর বিদুরের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। যদিও এইদুই ভাইয়ের থেকে বিদুর সর্বতোভাবে উপযুক্ত ছিল সিংহাসনের দায়ভার গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু শূদ্রা দাসীর গর্ভজাত হওয়ায় সে পেলোনা নিজের যোগ্য স্থান। মনে পড়ে সেই রাতের কথা? হঠাৎই দেখেছিলাম আপনাকে বিদুরের বাহুডোরে! মিথ্যে বলব না, শারীরিক সুখ না পাওয়া এই মাদ্রীর মধ্যেও সেইরাতে জেগে উঠেছিল অবদমিত কাম! তারপর সেই যেদিন শুনলেন যে ধৃতরাষ্ট্র পত্নী গান্ধারী গর্ভবতী, লহমায় নড়ে গেলো আপনার জমি। আর্যপুত্রকে সর্বতোভাবে বোঝালেন বনবাসে যাওয়ার জন্য এবং রাজিও করালেন তাঁকে। যাতে সকলের চোখের আড়ালে জন্ম দিতে পারেন দেবতার ঔরসজাত তাঁর সন্তানেরা। মুখচোরা স্বভাবের হলেও রাজ্য রাজনীতির গভীর নেপথ্য ষড়যন্ত্র বোঝার মত দূরদৃষ্টি আমার ছিল। আর্যপুত্রকে আক্ষেপ করে বলেছিলাম, আপনি না বললেও আমি জানি যে হস্তিনাপুর ছাড়ার কারণ দিদি। উনিই আপনাকে বাধ্য করেছেন একাজ করতে। কিন্তু আপনি কেন এই কাজ করেছিলেন সেটা উনি জানার চেষ্টাই করেননি। এরপর আর কী পরপর ঘটনাবলি এগিয়ে চলল আপনার লেখা চিত্রনাট্যের পাতা ধরে। জন্ম দিলেন কুরু বংশের উত্তরাধিকারের। জন্ম নিল আপনার আরও দুই পুত্র। তারপর একপ্রকার বাধ্য হয়েই আমার প্রতি সদয় হলেন আপনি। মা হলাম আমি। এরপর এক বসন্তের মনোরম সন্ধ্যায় এলো সেই অভিশপ্ত সময়। আর্যপুত্র এড়াতে পারলেন না আমার শারীরিক আকর্ষণ, ভুলে গেলেন নিজের মৃত্যুশাপ! সদ্য স্বামীহারা মাদ্রীর গগনভেদী কান্নার শব্দে ছুটে এলেন আপনি। মনের জ্বালা মিটিয়ে তিরষ্কারও করলেন। এই চুড়ান্ত কূটনৈতিক পরিবেশের মধ্যে যে আমি কখনও শান্তি পাবো না একথা আমি বুঝে গিয়েছিলাম। তাইতো নিজের সন্তানদ্বয়কে তুলে দিলাম আপনার হাতে। মিথ্যে বললাম যে, আপনার সন্তানদের মাতৃস্নেহ দিতে আমি অপারগ। আপনি যদিও সহমৃতা হওয়ার অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু আমি জীবনে প্রথম মাথা নোয়াইনি আপনার সম্মুখে। যাইহোক সব নগ্ন সত্যিকে অন্তরে নিয়ে আমি চলে গেলাম। এবার হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তনের পথেও আর তেমন বাধা রইল না। আসলে বেঁচে মরে থাকার চাইতে মরে বেঁচে যাওয়া শ্রেয়। তাই স্বামীর সহগামিনী হয়ে এই রাজনীতি আর অপমানের জীবন থেকে মুক্ত হলাম। তবে আমার রেখে যাওয়া এই চিঠি আপনাকে কখনও শান্তির যাপন দেবেনা। স্বস্তিও পাবেন না দিনান্তিকে।
বিদায়...
ইতি
মদ্ররাজকন্যা মাদ্রী।
গল্পাণু
তন্দ্রা কথা
রঞ্জনা বসু
নিত্য কত কি যে ঘটে, তার খবর কে রাখে ?
ষষ্ঠ তলার প্রনবকে পরোপকারী ছেলে বলে সবাই চেনে। তার চায়ের দোকানের আয়ে মা-ছেলের সংসার কোনরকমে চলে। সেই দোকানে এক কীর্তন গাইয়ে আসে ভিক্ষা নিতে, সঙ্গে তন্দ্রা নামের একটি মেয়ে। তার গানের গলাটি চমৎকার। প্রনব তার প্রেমে পড়ে।
একরাতে প্রনব তাকে বিয়ে করে আনলে, বিধবা মা আশীর্বাদ করে বউ ঘরে তোলে। তন্দ্রা সংসার সাজায়, রাঁধে-বাড়ে। উঠোনে আলপনা আঁকে, সেখানে চাঁদের আলো এসে পড়ে। মাঝে মাঝে কীর্তন গাইয়ে আসে, দেখা করতে। হঠাৎই তন্দ্রা নিখোঁজ হল।
প্রনব পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায়। বছর দুয়েক পর ভাঙ্গাচোরা এক আখরার পেছনের পুকুর থেকে একটা কঙ্কাল উদ্ধার হয়। লোকে বলে...
গল্পাণু
জ্বলন্ত সত্য
কেয়া নন্দী
মায়ের পছন্দ করা পাত্রী পাপিয়া’র সঙ্গে নিভৃতসাক্ষাতে চলেছে পলাশ। গন্তব্য ‘আদি সপ্তগ্রাম’ -- ওখানের-ই হাইস্কুলের শিক্ষিকা।
মাঝে মধ্যে কেনার সুবাদে হকার সমীরের সঙ্গে আলাপ আছে। নির্দিষ্ট স্টেশনে নেমে পলাশ বলে, সমীর ‘আদি সপ্তগ্রাম হাই স্কুল’ টা কোথায় ?
স্কুল থেকে ছেলেটাকে নিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। অগত্যা ঐ স্কুলে যেতে হলো।
শিখা না ? এই স্কুলে পড়াস ?
হ্যাঁ, এম.এ. পাশ করার পর টেট উত্তীর্ণ হয়ে এই প্রাইমারি স্কুলে।
তুই ? পলাশ বলে, বর্ধমানের একটি কলেজে পড়াই।
শিখার মুখেহাসি। পলাশ একটু থমকে যায়। ঐ হাসিতে কি কিছু ইঙ্গিত ছিল ! ওকি জানে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সত্য’ স্যারের কাছে পি.এইচ.ডি করছি !
চলুন স্যার।
আসি রে। পলাশকে যেতে দেখে শিখা’র চোখটা হঠাৎ-ই করকর করতে লাগলো।
পথে যেতে যেতে পলাশেরও স্মৃতির ‘শিখা’ জ্বলে উঠলো ।
উপন্যাস
বসতভিটা
পর্ব -২
শুভাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
শেষমেশ নীলিমার অনুরোধ ফেলতে না পেরে এবং কতকটা আমাদের কথায় একপ্রকার রাজী করানো গেল রমাকে।
আমি আর জহর হলাম চায়ের পোকা। পাঁচ দশ মিনিট দেরী হয় হোক,বেড়াতে এসে খোলা আকাশের নীচে চায়ের দোকানে না ঢুকলে বেড়ানোর মজাটাই যেন তেতো হয়ে যায়। একএক সময় জহরও মজা করে বলে..' দেখেছেন দাদা, জহুরি ঠিক আর এক জহরকে চিনে নেয়...পেয়েছি বটে আপনাকে...!'
হয়তো অনেকটা এ কারণেই আজ আমার বেয়াইটি শুধু যে আমার পরম আপনজন তা ই নয়, এমনতরো মনের মিল সচরাচর বোধহয় খুঁজে পাওয়া ভার। এর মাঝে অবশ্য আমাদের দলে যদি রাখাল এসে পড়ে, তাহলে বেড়ানোর আনন্দ ষোলো আলার মধ্যে আঠারো আনাই সফল।
স্টেশনের একধারে ফেন্সিংএর পাশে টিনের ছাউনি দেওয়া গুমটির ভেতর এক বুড়ো চা বিক্রি করছিল। আমরা এগিয়ে গেলাম।
রাখাল ব্যস্ত হয়ে বললো,' তাড়াতাড়ি ছয় কাপ চা বানান। দেখুরিয়া যাবো। প্রায় এক ঘন্টার কাছাকাছি পথ..'
খক খক করে করে কাশতে কাশতে বুড়োটা জিজ্ঞেস করলো..' দেখুরে গ্রাম? কিসে যাবেন? অটো, ট্রেকার আজ আর হয়তো কিছুই চলবে না...কি জানি। ঐ খানকতক রিকশা দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যান্ডে। দোকানপাটই তেমন একটা খোলে নি তো যানবাহন...'
' এরকম অবস্থা কেন গো আজ?'
জিজ্ঞেস করলো রাখাল।
' যদু শ্যাকরা মরে গেছে...রামপুরহাট পরিবহন, ব্যাবসায়ী সমিতির বহু পুরোনো লোক...গাড়ি ভাড়া খাটাতো, আবার দোকানও চালাতো.. কত আয়োজন করে ফুল চন্দন দিয়ে সাজিয়ে শ্নশান ঘাটে নিয়ে যাওয়া হলো...সেই কারণেই বারো ঘন্টার বাজার বন্ধ। এই তো ছটার পর আবার খুললাম...কি করবো, আমরা তো আর যদু শ্যাকরা নই...যা দুচারপয়সা ক্ষুদকুরো আসে তা ই লাভ...এসে তো দেখছি সত্যিই মরা বাজার...অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছি....শেষবেলায় কটা লোকই বা আমার মতো ঝাঁপি খোলে...আপনাদের দিয়ে বউনি করলাম...রিকশা পেয়ে যাবেন...কপাল ভালো থাকলে ট্রেকার...কোত্থেকে আসছেন বাবারা?'
চা পান শেষে ধূমপানের আমেজ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি শুনশান না হলেও আশপাশে লোক বেশ কম। কিছু দোকানপাট খোলা। তারা বলতে গেলে মাছি মারছে...বেশিরভাগ ঝাঁপিই বন্ধ। চা ওলা বু্ড়োটা ভুল বলে নি। বাজার অঞ্চল বলেই হয়তো স্ট্যান্ড থেকে চারটে রিকশা পেয়ে গেলাম। অটো বা ট্রেকারের জন্য অযথা সময় ব্যায় না করে আমরা এক একটা রিকশায় দুজন করে উঠে পড়লাম।
স্টেশন সংলগ্ন এলাকা ধরে কিছুটা যাবার পর গ্রামের রাস্তার দিকে মোড় ঘুরলো আমাদের রিকশা। একটু আগেও যা দুচারজন মানুষ যাতায়াতের পথে চোখে পড়েছিল এখন আর জনপ্রাণী নেই বললেই চলে। খেত খামার, ধূ ধূ মাঠ, গাছপালায় ঘেরা ছোট ছোট গ্রামকে দুপাশে রেখে মাঝবরাবর আলের মতো পিচঢালা রাস্তা চলে গেছে বহুদূর...ঝোপঝাড়, গাছগাছালির ভেতর থেকে দূরে দূরে টিমটিমে আলো জ্বলা ছোট ছোট কুঁড়েঘর, মনুষ্য বসতি...রেল স্টেশনকে পেছনে ফেলে এসেছি অনেকক্ষণ... শুধু দূর থেকে ট্রেনের হুইসিলের ক্ষীয়মাণ আওয়াজ ভেসে আসে কানে...জ্যোৎস্নার আলো চিকচিক করছে পুকুর, বাঁওড়ের জলে, বাঁশ ঝাড়, লতাপাতায়, ক্ষেতের আলে, আমাদের পথ চলার আগে আগে....অনেকক্ষণ পর পর একটা কি দুটো ভ্যান রিকশা,পথচারী ছায়াশরীরের মতো চলে যায় পাশ দিয়ে....ধূ ধূ মাঠ, ধানক্ষেত পেরিয়ে আসা শিরশিরে হাওয়া গায়ে লাগছে বেশ...একরাশ কুয়াশার মতো ধোঁয়াটে বাতাস উড়ে বেড়াচ্ছে এদিক সেদিক...সেই ধোঁয়াশার আড়ালে ঢাকা দূরের গাছপালাগুলো আবছায়া অবয়বের মতো যেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আমাদের দিকে...অদ্ভুত সব অবয়ব যেন...যার মাঝখানটা কুয়াশায় ঘেরা...শুধু মাথাগুলো উঁকি মেরে চেয়ে রয়েছে...
আমি আর জহর একই রিকশায়। যেতে যেতে সে আমায় বলে,'আমার রেডিয়াম ডায়ালে বলছে সবে রাত আটটা। তেমন জোড়ালো শীত না পড়তেই চারিপাশ কিরকম নিশুতি হয়ে গেছে দেখছেন...নভেম্বরের এই সময়টা থেকে কুয়াশার মতো ধোঁয়া গুলো এসে জড়ো হয় মূলত ফাঁকা পল্লী অঞ্চলে...বেশ থ্রিলিং কি বলেন?'
' যা বলেছো?'
' হালকা চাদর টাদর নিয়ে এসেছেন তো? বেশ বেশ...। ভোরবেলা রাখাল, আমি, আপনি মিলে নদীর আশপাশটা ঘুরে আসা যাবে...যাকে বলে অ্যাট দ্য ডন...ঐ সময়কার দৃশ্য, সে আর একরকম..ও ভাই, আর কত পথ বাকি?'
ভোরবেলাকার গ্রাম দেখার ঔৎসুক্যটা আপাতত অবদমিত রেখে অন্তরাত্মা যেন নৈশ প্রকৃতির মাঝেই ডুব দিল আবার। জোয়ান রিকশা চালক অন্ধকারে যতটুকু জোরে চালানো যায় হয়তো তার চেয়ে কিছু বেশি জোরেই টেনে নিয়ে চলেছে আমাদের। একবার মনে হলো,জিজ্ঞেস করি..আর কতক্ষণ। বললাম না। সময়টুকু ফুরিয়ে গেলেই তো গেল। এমন মুহূর্ত খুব বেশি বোধহয় পাওয়া যায় না....
পেরিয়ে যাচ্ছে ছায়া ছায়া গ্রাম, বন ঝোপ, জোনাকি জ্বলা আলের ক্ষেত, তাল,নারকেল,বাঁশ গাছের সারি, আরো কত কি....সামনের তিনটে রিকশা আমাদের ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে...একাকি গ্রাম্য পথে চাঁদের আলো ছাড়াও আরো একটা জিনিস আমাদের সঙ্গ নিয়েছে অনেকক্ষণ ধরে.... সেটা হলো আঁকা বাঁকা রাস্তা ধরে ছড়িয়ে থাকা উড়ো খই...পিচ ঢালা রাস্তাকে পেছনে ফেলে যখন থেকে আর একটা মেঠো রাস্তায় মোড় ঘুরেছে রিকশাটা তখন থেকেই রাস্তা জুড়ে এই খইগুলো লক্ষ্য করে আসছি...চাঁদের আলোটুকু না থাকলে হয়তো চোখেও পড়তো না....যেতে যেতে হঠাৎ সেই বুড়ো চা ওলার মুখে শোনা যদু শ্যাকরার মৃতদেহ নিয়ে যাবার কথাটা সন্ধ্যাকাশে যেন হাওয়ায় উড়ে এলো মনে...অন্য কারো শবদেহও তো যেতে পারে...তবু কি জানি কেন ঐ অচেনা অজানা নামটুকুই ঘুরপাক খেলো বেশ কয়েকবার, ধোঁয়াশায় ঘেরা নিঃস্তব্ধতার মাঝে।
চা খেতে খেতে রাখাল বলছিল, তাদের গ্রামের দুটো গ্রাম আগে যদু শ্যাকরার বাড়ি...অনেক কালের পুরোনো ব্যাবসায়ী...রাখালের বাবা ছেলে মেয়েদের বিয়ের গয়না সব ওর কাছ থেকেই...
খই ছড়ানো সরু রাস্তাটা একটু পরেই ঝুপসি অন্ধকারে গাছপালার আড়ালে মিশে গেল। আমাদের রিকশা গুলো ও রাস্তায় না গিয়ে একটা লাল মাটির পথ ধরলো। সামনের রিকশা থেকে রাখাল বেশ জোরে বলে উঠলো..' আর পাঁচ মিনিটের রাস্তা বেয়াই....'
উপন্যাস
চেনা ভয় অচেনা আপোষ
অয়ন দাস
পর্ব - ১
বছরের ঠিক মাঝখানে আমি দুম করে আমার অতদিনের ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিলাম।কিছু ছাড়তে গেলে এরকম দুম করেই ছাড়তে হয়।আসলে দুম করে বললেও ঠিক দুম করে নয়।আমার মনের ভিতর ছেড়ে দেওয়ার ভাবনাটা সঞ্চারিত হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগেই।অনেকদিন আগেই কাজের জায়গা থেকে আমার মন উঠে গেছিল।
তখন আমি কোভিডে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে শুয়ে রয়েছি।গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে।এদিকে আমার রিজিওনাল ম্যানেজার ও জোনাল ম্যানেজার আমাকে ক্রমাগত ফোন করে যাচ্ছে,আজ ব্যবসা কত হবে।কতখানি অমানবিক হলে এটা সম্ভব! দুদিন বাদেই আমি একটি মেল পেলাম যেখানে লেখা রয়েছে আমার দুটি পারফর্মিং হেড কোয়ার্টার আমার থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে এবং একটি নতুন নন পারফর্মিং হেড কোয়ার্টারকে আমাকে দেওয়া হয়েছে।সেদিনই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আমি ছেড়ে দেব এই চাকরি।
একজন বিকৃত মনস্ক মানুষের কাছাকাছি থাকলে অন্য মানুষটির ব্যক্তিত্বতেও তার আঁচ পড়ে। আমিও ক্রমশ যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম।
এক সর্বগ্রাসী ভয় আর অনিশ্চয়তা আমাকে ক্রমশ চেপে ধরছিল।
এখন মুশকিল হল চাকরি ছেড়ে দিলে আমার চলবে কি করে! মাসের এক তারিখে আমার মোবাইলে টুং করে একটা শব্দ হয় এবং একটি বিরাট অঙ্কের টাকা আমার একাউন্টে ঢোকে,চাকরিটা চলে গেলে সেটার কি হবে?
সুতরাং নতুন একটি চাকরি না পেয়ে এই চাকরি ছাড়ি কি করে?
মানুষ দু'বার চাকরি ছাড়ে।যেকোনো কাজই মানুষ দু'বার করে। একবার যখন সে সিদ্ধান্ত নেয় এবং আরেকবার যখন সে সিদ্ধান্ত এক্সিকিউট করে।
একটা চাকরি ছাড়া মানে তো শুধু একটা চাকরি ছাড়া নয়,একটা চাকরি ছাড়া মানে দীর্ঘ দিনের একটি অভ্যাসকে পরিত্যাগ করা।দীর্ঘদিনের একটি সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার যন্ত্রণাকে সহ্য করা এবং সর্বপরি একটি অজানা অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে চলা।
এক এক দিন খুব ভোরে আমার ঘুম ভেঙে যেত।একসঙ্গে চা খাওয়ার পর আমি এবং রুমা, আমাদের মেয়ের একটি খাতা আর পেন নিয়ে হিসেব কষতে বসতাম।ঠিক কত টাকা রোজগার হলে আমাদের সংসার চলে যাবে।আমাকে মাসের মধ্যে তিনটি সপ্তাহ বাইরে বাইরে কাটাতে হত।রুমা ভীষণভাবে চাইছিল আমি ঘরে থাকি।
এবার আমি হিসেব করতে বসলাম আমার জমানো টাকা কত।কত টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করলে কত টাকা সুদ পাবো।
সত্যি বলতে কি এতদিন শুধু গাধার মত পরিশ্রম করে গেছি।কলু'র বলদের মত কোম্পানির বেগার খেটে গেছি।আর কিচ্ছু চিন্তা করিনি।
আকস্মিকভাবে খেয়াল করলাম আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডে আমার একাউন্ট নম্বর ভুল থেকে গেছে,এতদিন খেয়াল করিনি।শুরু করলাম একনাগাড়ে ফলো আপ।
কোনো জায়গা থেকে মন উঠে গেলে সেই জায়গাটা বড় অসহ্য হয়ে যায়।আমার ইচ্ছে করছিল চাকরি নামক বস্তুটিকে দুই হাতের মধ্যে নিয়ে এসে গলা টিপে মেরে ফেলি এবং মেরে ফেলার আগে তার মুখে পেচ্ছাপ করে দিই কিন্তু সেটা পারছিলাম না কারণ আমার পেটের ভাত ওই চাকরির টাকাতেই চলে।চাকরিটা ছাড়বো ছাড়বো করে কিছুতেই আর ছাড়া হচ্ছিল না।
বহরমপুর গেছি অফিস ট্যুরে, দুদিন পরেই মিটিং, একগাদা পেপার ওয়ার্ক্স। হোটেলের ঘরে বসে সেই পেপার ওয়ার্ক্স গুলো করতে গিয়েই আমার মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠলো, এনাফ ইজ এনাফ।চলো এবার সম্পর্কটা শেষ করে দেওয়া যাক।
আমার দু একজন বন্ধু'কে ফোন করলাম। যা করছি ঠিক করছি তো? হাতে কোনো চাকরি নেই।একটা বিরাট রিস্ক হয়ে যাচ্ছে না তো?
পরেরদিন বহরমপুর থেকে বাড়ি ফিরে এসে মা,বাবা ও স্ত্রীকে একসঙ্গে বসিয়ে আমার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলাম।তিন জনেই বলল,এক্ষুনি এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসো।মা বললেন, তুই আগে চাকরি ছাড়,বাকিটা আমি বুঝে নেব।বাবা বললেন, যে চাকরি তোকে মানসিক যন্ত্রণা দিচ্ছে কী লাভ সেই চাকরি করে।স্ত্রী বলল,কিছু একটা ঠিক হয়ে যাবে,তুমি আগে চাকরি ছাড়ো।
পরের দিন রেজিগ্নেশন লেটার পাঠিয়ে দিলাম। মেইলটা করার পর আমার বুক থেকে যেন এক পাষাণ ভার নেমে গেল।আমার নিজেকে মনে হতে লাগল মুক্ত বিহঙ্গ। আমি নদীর তীরে চলে গেলাম।কোনো কারণ ছাড়াই একটি নৌকা ভাড়া করে গঙ্গার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত গিয়ে আবার ওপার থেকে এপারে এলাম।তারপর আবার এপার থেকে ভেসে যেতে লাগলাম ওপারে।
এদিকে আমার সিনিয়র'রা একটানা আমাকে ফোন করে যাচ্ছে কিন্তু একটা ফোনও আমি রিসিভ করছি না।অনেক গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্ধেক হয়ে পড়ে আছে।ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট কিছু অ্যাসাইনমেন্ট আছে আজ।দুদিন পরে রিভিউ মিটিং, তার প্রস্তুতি আছে।
খবরটা ছড়িয়ে গেছে, আমার ফোনে একের পর এক ফোন আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে।
আমাকে ফোন করছেন আমার ইমিডিয়েট বস,তার বস,তারও বস।মোবাইলে একের পর এক হোয়াটসঅ্যাপ আসছে।
আমার মাথার উপর অনন্ত আকাশ,দুপাশে সবুজ বনানী, নদীতে এখন জোয়ার, আমি ভেসে চলেছি সেই স্রোতস্বিনী গঙ্গার উপর দিয়ে।
আমি অট্টহাসিতে ফেটে পড়লাম। মনে মনে বললাম, এতদিন আমাকে নিয়ে অনেক খেলেছো তোমরা।
এবার আমি খেলবো।
ক্রমশ...
গল্প
(১)
শহরের এক সরকারি হাসপাতালের বেঞ্চে ব’সে প্রহর গুনছে গুল্লু। উদ্বিগ্ন চোখে বারবার দেখে নিচ্ছে দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটা। প্রতিটা কাঁটায় খেলা করছে তার বাবার জীবন-মৃত্যু।
“এখানে গুলশন শর্মা কে আছেন?”
“ডাক্তার বাবু, হামি আছি।”
“আপনার বাবাকে এখানে ফেলে রাখবেন না। রেফার করে দিচ্ছি, এখনই কলকাতার কোনও সুপারস্পেশালিটি হসপিটালে নিয়ে যান। এখানে নিউরো সার্জেন কেউ নেই। আর ব্রেইনের ব্যাপার, সময় নষ্ট করাটা ঠিক হবে না।”
গুল্লু কাঁদতে কাঁদতে বলল, “ডাক্তার বাবু হামি এতো টাকা কোথায় পাব! পেরাইভেট আসপাতাল তো বহত খরচ আছে। হামি সামান্য লাপিত…”
“আচ্ছা ঠিক আছে, কেঁদো না। তোমার সেলুনে তো অনেক বড় মানুষও আসেন মাঝে মাঝে! তুমি তাঁদের বলো, আর এদিকে আমিও একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। তাহলে মনে হয় আপাতত ট্রিটমেন্ট করতে অসুবিধা হবে না।”
ডাক্তার সেনের কথাগুলো শুনে গুল্লু মনে করার চেষ্টা করল কে কে তার সেলুনে আসেন। বিদ্যুৎ গতিতে একটা মুখ তার চোখে ভেসে উঠছে। এই এলাকার বিশিষ্ট সাংবাদিক, দেবব্রত রায়। তিনি একটি বিখ্যাত দৈনিক খবরের কাগজের অনেক পুরোনো সাংবাদিক। গুল্লুর কাছে মাঝে মাঝে আসেন চুল-দাড়ি কাটতে। গুল্লুর হাতের কাজ নাকি শহরের অনেক বড় বড় পার্লারকেও টেক্কা দেয়! তাই, এখানে তিনি আসেন, গুল্লুর হাতের নৈপুণ্যের কারণে। গুল্লু এক মুহূর্তও ব্যয় না ক’রে ফোন করল দেবব্রত রায়কে। ফোন ব্যস্ত বলছে। এখন দেবব্রত বাবুর ব্যস্ততার থেকেও গুল্লুর বাবার জীবনের দাম বেশি। দেবব্রত বাবুর ব্যস্ততার তোয়াক্কা না ক’রে গুল্লু আবার ফোন করল দেবব্রত রায়কে। এবার রিং হচ্ছে ফোনে…
(২)
সকাল আটটার সূর্য রশ্মি বোর্ডের ওপর পড়লেই, খুলে যায় ‘গুল্লু হেয়ার কাটিং শপ’। এলাকায় সাত-আট বছর ধ’রে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে গুল্লু। উত্তর প্রদেশ থেকে সেই কোন কালে সীতারামপুরে উঠে এসেছিলেন গুল্লুর বাবা, চিনু শর্মা। তারপর, ইট ভাটায় দিন মজুরের কাজ ক’রে সামলেছেন নিজেকে নিয়ে দশজন সদস্যের ভরা সংসার। গুল্লুর জন্ম এখানেই। তাই, টেনে টেনে হলেও ভালো বাংলা বলতে পারে সে।
“এই গুল্লু, কজন আছে রে?”
“সমীর দা’র পোরে আরও দুইজোন।”
“দে, আজকের পেপারটা দে। যতক্ষণ আমার নম্বর আসছে, ততক্ষণ পড়ি।”
“কোনটা দিব? বাংলাটা না আংরেজিটা?”
“বাংলাটাই দে। সকালে ইংরেজি নিয়ে বিশেষ বসি না…”
শিবদাস বাবুর কথা শুনে গুল্লু আয়না দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল। এখানে সবাই গুল্লুর সাথে হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক রেখেছে। গুল্লুর বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ হলেও, সে প্রায় তার বাবার বয়সী লোকেদের সাথেও মিশে যেতে পারে অনায়াসে।
“না, বাংলাটায় সেই একই খবর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, আর যতটুকু আছে সেটাও বিজ্ঞাপনের দয়ায় অল্প জায়গা ক’রে নিয়েছে। তুই বরং আমায় ইংরেজিটাই দে”- কথাগুলো বিরক্তিভরা মুখে ব’লে উঠলেন শিবদাস বাবু।
গুল্লু মুচকি হেসে এগিয়ে দিল ইংরেজি সংবাদপত্র। সে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি তিনটে ভাষার কাগজই রাখে। দোকানে কাস্টমার না থাকলে সে নিজেই পড়ে হিন্দিটা, মাঝে মাঝে ইংরেজিও। চেষ্টা করে বোঝার। অল্প শিখেছিল স্কুলে পড়ার সময়। তাই, একেবারে অজানা ভাষা নয় এটা তার কাছে।
“ছেলের রেজাল্ট বেরিয়েছে মাধ্যমিকের। এইট্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস পেয়েছে। এই নে মিষ্টি খা…” --সামনের মিষ্টির দোকানের লাল্টু দা এক প্যাকেট কালাকাঁদ নিয়ে এসেছে গুল্লুর জন্য। সন্তানের সাফল্যে বাবারাও বাচ্চাদের মতো আনন্দ করেন। এইরকম নির্ভেজাল আনন্দ দেখতে বেশ ভালোই লাগে!
“বাহ! দারুণ বেপার আছে লাল্টু দা’। তোবে, শুধু মিষ্টিতে চোলবে না। মুর্গা খাওয়াও একদিন।”- গুল্লুর চোখেও খুশি ঝিলিক দিচ্ছে।
গুল্লুও মাধ্যমিক দিয়েছিল। টিউশন ছিল না তার। বাবার সামর্থ্যে কুলোয়নি। কিন্তু, কোনও গাইডেন্স ছাড়াই সে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছিল। স্কুলের শম্ভু মাস্টার অবশ্য খুব সাহায্য করেছিলেন তাকে। পাশ করেই সে স্যারকে প্রণাম করতে গিয়েছিল। স্যার বলেছিলেন, আরও পড়তে। সাহায্যও করতে চেয়েছিলেন গুল্লুকে, কিন্তু সে নিতে রাজি হয়নি। স্যারের নিজেরই তিনটে বড় বড় মেয়ে ছিল। তাদের বিয়ে দিতেই স্যারের অবস্থা খারাপ। তাই, গুল্লু নিজের বোঝা স্যারের কাঁধে চাপাতে চায়নি।
হাতের কাজ শেষ করে টিফিন খেতে বসল গুল্লু। দুপুর বারোটার আগে কোনোদিনই সকালের খাওয়া জোটেনা তার। সবই কপাল! কিন্তু, এত দুঃখের মাঝেও যখন সে নিজের মেয়েকে পড়তে দেখে, শান্তি পায় ও। কষ্ট ক’রে হলেও সে নিজের মেয়েকে পড়াবে। ডাক্তার বানাবে। গুল্লুর জীবন রুটির পোড়া অংশের মতো হলেও, সে তার মেয়ের জীবন করবে সাদা অংশটার মতো; ঝকঝকে এবং মসৃণ।
(৩)
“ধুর, এই মাল কেন আবার ফোন করছে? এই বিপিএল ক্যাটাগরিগুলোর জন্য হয়েছে যত জ্বালা। সুযোগ খুঁজতে ওরা ব্যস্ত থাকে।”-এই কথা গুলো মনে মনে ব’লে রাগে গজগজ করতে করতে গুল্লুর ফোন তুলল সাংবাদিক দেবব্রত রায়।
“হ্যালো…কে?”
“দাদা, হামি গুল্লু আছি। হাপনার সোঙ্গে কোথা ছিল…”
“হুম গুল্লু, বল…”
“দাদা, হামার বাবুজির এক্সিডেন্ট হ’য়ে গিছে। বাইকে ধাক্কা লেগে গিছে। মাথায় চোট এসেছে। সরকারি ডাক্তারবাবু বলছে পেরাইভেটে নিয়ে যেতে হবে কলকাত্তায়…আপনি রিপোর্টার আছেন, কিছু একটা বেবস্থা কোরেন…”
কথাগুলো বলতে বলতে ফোনেই কান্নায় ভেঙে পড়ল গুল্লু। দেবব্রত রায় তাকে বরাবর বলেছেন তিনি তার পাশে আছেন। সেই ভরসাতেই দেবব্রতবাবুকে ফোন করেছে গুল্লু।
“গুল্লু, আমার রেফারেন্সে কী হবে বল! তুই বরং এসডিও অফিস থেকে চিঠি নিয়ে আয়। ওঁরা বললে যে কোনও নার্সিং হোম ভর্তি ক’রে নেবে। টাকা নিয়েও চাপ হবে না। সেরকম হ’লে তুই পাঁচ-দশ হাজার আমার থেকে নিয়ে নিস পরে।”
দেবব্রত রায়ের এই কথাগুলো শুনেই গুল্লু বুঝল সব মিথ্যে। সাংবাদিকরা নেতাদের বিরোধিতা করলেও, এঁরা ওঁদেরই মতো। এঁদেরও পাল্টি খেতে দুদিন লাগেনা।
“হাপনি একটা চিঠি লিখে দিবেন দাদা? নইলে, এসডিও অফিস হামাদের হোটাৎ ক’রে ঢুকতে দিবেনা। দয়া কোরেন মাই বাপ হামার। বাবুজি মরে যাবে নইলে!”
নাহ, গুল্লুকে এড়ানো যাবে না। একটা চিঠি লিখে দিলেই যখন আপদ বিদেয় হবে, তাহলে খুব একটা অসুবিধে নেই। তারপর তার বাবার চিকিৎসা হোক বা না হোক কে দেখতে গেছে? সামনে ইলেকশন, সেই নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট - কথাগুলো ভেবে নিয়েই দেবব্রতবাবু বললেন, “ঠিক আছে, এসে নিয়ে যা বাড়ি থেকে। আধঘণ্টার মধ্যে আয়। নাহলে, আমায় পাবিনা।”
আধা ঘণ্টার মধ্যে কোথাও যাওয়ার নেই দেবব্রতবাবুর। গুল্লুকে এড়িয়ে যেতেই এই কথাগুলো বলা। তবে, গুল্লুও নাছোড়বান্দা, আধা ঘণ্টার আগেই পৌঁছে গেছে দেবব্রতবাবুর বাড়ি।
তাকে এত তাড়াতাড়ি দেখে একটু চমকেই গেছিলেন দেবব্রত রায়। বুঝেছিলেন গুল্লুর দরকারটা। তাই, বেশি কথা না বাড়িয়ে চিঠিটা দিয়ে দেন তাকে। এবার বুঝে করুক গুল্লু। আর কোনও দায়িত্ব নেই দেবব্রত রায়ের। ইলেকশনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী আসছেন জেলায়, তাই নিয়ে তাঁকে আর্টিকেল লিখতে হবে খবরের কাগজের জন্য। সেটা নিয়ে ব্যস্ত হ’য়ে পড়াতেই বেশি আনন্দ। গুল্লু নিজেরটা বুঝে নিক…
(৪)
মিডিয়া লেখা চার-চাকা গাড়িটা এসে দাঁড়ালো গুল্লুর দোকানের সামনে। গুল্লু দেখেই বুঝতে পারল কে এসেছে, কিন্তু চুল-দাড়ি কাটার থেকে মন সরালো না। গাড়ি থেকে নেমে এলেন একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। এই এলাকার বিখ্যাত সাংবাদিক দেবব্রত রায়। গুল্লু একটু নড়েচড়ে দাঁড়াল। কারণ, এইরকম পেল্লায় শ্যুট-বুট পরা কেউ এলে তাঁরা লাইনে বসতে চান না। তাঁদের ভিআইপি পরিষেবা দিয়ে আগে সেবা করতে হয়। আর, দেবব্রত রায় এই এলাকার বেশ বড় নাম, তিনি গুল্লুর দোকানে আসেন সেটাই গুল্লুর ভাগ্য, তাঁকে বসিয়ে রাখা কোনোদিনই উচিৎ না। দেবব্রত রায় কিছু না ব’লে গম্ভীর হ’য়ে বসলেন। ঘাড়টা এদিক-ওদিক একটু ঘুরিয়েই গুল্লুর দিকে উদ্দেশ্য ক’রে বললেন, “চুলটা সাইড থেকে ছেঁটে দিস আর দাড়িটা…” তিনি কথা শেষ করতে না করতেই গুল্লু ব’লে উঠল, “হাঁ স্যার, হামার মালুম আছে হাপনার ইস্টাইল। দু-মিনিট বোসেন স্যার, আমি ইনাকে ছেড়েই হাপনাকে ধরছি।”
আজ কিছু উপরি ইনকাম হবে গুল্লুর। সত্তর টাকার চুল-দাড়ি ছাড়াও আরও কিছু টাকা টিপ হিসেবে দেন দেবব্রত বাবু। বড়লোকেরা যত ছড়াবেন, তত গুল্লুর মতো মানুষদের লাভ। মেয়ের জন্য জ্যামিতি বাক্স, আঁকার বই, পুতুল ইত্যাদি কেনা যায়।
“তোর হাতে জাদু আছে রে, গুল্লু। তাই তো এখানে আসি।”
“ই হামার ভাগ্য আছে স্যার। হাপনার পায়ের ধূলি পড়ছে হামার দুকানে…”
“নে, রাখ একশো টাকা। বাড়িতে যাওয়ার সময় মিষ্টি নিয়ে যাস।”
গুল্লু জানত এইরকম হবে। দেবব্রত রায় মানেই এক্সট্রা ইনকাম। আজ মেয়েটা খুব খুশি হবে। অনেকদিন ধ’রে জ্যামিতি বাক্স চাইছিল। এবার সে সেটা পেয়ে স্বর্গ পাবে। মেয়ের হাসি মুখটা মনে পড়তেই গুল্লুর মন আনন্দে ভ’রে উঠল।
“আর, কখনও কিছু লাগলে বলিস।”
“হাঁ স্যার, একদম বোলব…”
মুদির দোকানের ভোলা সবটা দেখে দৌড়ে এল গুল্লুর কাছে। এক্সট্রা ইনকাম দেখলেই তার মদ খাওয়ার ধান্দা চলতে থাকে। কিন্তু, আজ গুল্লু এটা দিয়ে মদ খাবে না। এই টাকা আজ তার মেয়ের জ্যামিতি বাক্সের জন্য বরাদ্দ। নিজের ফুর্তির চেয়ে মেয়ের ভবিষ্যৎ বেশি গুরুত্বপূর্ণ গুল্লুর কাছে।
(৫)
এসডিও অফিসে প্রচুর ভিড়। দুনিয়ার সমস্ত বিপদ আজ এসে জড়ো হয়েছে মানুষের জীবনে। গুল্লু দাঁড়িয়ে আছে চাতক পাখির মতো। চোক-মুখ ব’সে গেছে ক্ষিদে-তৃষ্ণায়। গুল্লুর নম্বর দশ। ন’ নম্বর মানুষের সাথে দেখা করছেন এসডিও শুভ্র মজুমদার। ন’ নম্বর লোকটাকে বেরিয়ে আসতে দেখেই গুল্লুর আনন্দ হল। এইবার তার নম্বর।
“এই দাঁড়াও, এখন আর হবে না। এবার কাল।”- এক লম্বা চওড়া দারোয়ান গুল্লুকে প্রায় ধাক্কা মেরে এই কথা বলল।
“হামার আজ দোরকার আছে, হামার বাবুজিকে নার্সিংহোম লিয়ে যেতে হোবে…”
“আরে, এসডিও সাহেব এখন অফিসের কাজে বাঁকুড়া যাবেন। আজ আর হবে না।”
“আজ না হ’লে, হামার পিতাজি মরে যাবে…দয়া করো মুঝে। অন্দর জানে দো মুঝে…”
“হ্যাট, আজ আর হবে না, ভাগ এখান থেকে। শালা, বুড়ো মরলেও কী আর বাঁচলেও কী! যেন জোয়ান ছোকরা…”
প্রায় ধাক্কা মেরে গুল্লুকে মাটিতে ফেলে দিল দারোয়ান। গুল্লু তার সাথে শরীরে পারবেনা। গুল্লু নিজের মাতৃভাষা হিন্দিতে, “মুঝে জানে দো, মুঝে জানে দো”- বলতে বলতে কেঁদে ফেলল। বিপদের সময় মুখে মাতৃভাষা নিজের থেকেই চ’লে আসে, তা হয় তো গুল্লু সেই সময় খেয়াল করেনি! হাক্লান্ত হয়ে গুল্লু সরকারি হাসপাতালে ফেরত এল। দেবব্রত রায় আর ফোন তুলছেন না গুল্লুর। ডাক্তার সেনের দয়ায় এখনও সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তার বাবার। কিন্তু, বেশিক্ষণ এখানে ফেলে রাখলে বুড়ো বাপের প্রাণটা চ’লে যাবে।
“কোনও সুবিধা হল?”-ডাক্তার সেনের এই প্রশ্নের উত্তরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা ছাড়া আর কিছু করণীয় ছিল না গুল্লুর। ডাক্তার সেন সব বুঝে ঘড়ির দিকে তাকালেন। সন্ধে সাতটা বাজে। খুব বেশি হ’লে আর চার ঘণ্টা। তারপর…চিনু শর্মার অবস্থা একদম শেষের দিকে চ’লে যাবে।
(৬)
জ্যামিতি বাক্স নিয়ে বাড়ির দিকে পৌঁছাতেই গুল্লু ভিড় দেখল। সে ভাবল হয় তো কেউ মদ খেয়ে মাতলামি করছে বা বমি করছে! বস্তি অঞ্চলে এগুলো খুবই সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু, আজকের জটলাটা অন্যরকমের। কান্নাকাটির আওয়াজে চতুর্দিক ভ’রে গেছে।
গুল্লু সাইকেলটা নিয়ে একটু এগোতেই দেখল, তাঁর বাবা চিৎ হ’য়ে পড়ে আছে মাটিতে। মাথার পেছন দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে রক্ত। সত্তরের কাছাকাছি বয়সের চিনু শর্মা অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে শুয়ে।
“বাবুজি, ক্যায়সে হুয়া ইয়ে সব? রেশমা, এ রেশমা, ইয়ে সব ক্যায়সে?”- গুল্লু চিৎকার ক’রে জিজ্ঞেস করল তার স্ত্রীকে।
তার স্ত্রী বাকরুদ্ধ হ’য়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির দরজায়। গুল্লু আসার দু-মিনিট আগেই ঘটেছে ঘটনা। তাই, তাকে ফোন করার সময় পায়নি রেশমা। চিনু শর্মার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার নাতনি রিঙ্কি। সে কেবল তার দাদাজিকে উঠে বসার অনুরোধ করছে। দশ বছরের মেয়ে হতবাক এইরকম অবস্থা দেখে। চিনু শর্মা রাতের খাওয়ার পর হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। তখনই তিনজন যাত্রী সওয়ার একটা বাইক ফুল স্পিডে এসে তাকে ধাক্কা মারে। ব্যাস… তারপর সেই আওয়াজ শুনে লোকজন ছুটে আসে। কিন্তু চেষ্টা করেও কেউ বাইকটাকে আটকাতে পারেনি। আর, রাতের বেলা আলো কম হওয়ায় নম্বর প্লেটটাও দেখে উঠতে পারেনি কেউ। গুল্লু বুঝেছে এগুলো কোনও মাতালের কাজ। মদ খেয়ে ফেরার সময় ঘটিয়েছে এই দুর্ঘটনা। এই এলাকাটা মাতাল আর চরিত্রহীনে ভ’রে গেছে। বাবাকে একা বেরোতে দেওয়াই তাদের ভুল হয়েছিল। কিন্তু, তার বাবা তো নিজেই সব কাজ করতে ভালোবাসেন, তাই তাঁকে বাধা দেওয়া যায় না কোনোকিছুতেই। তবে, আজকের ঘটনার জন্য নিজেকেই বারবার দোষ দিল গুল্লু।
পুঁটিরাম খুব তাড়াতাড়ি কোথা থেকে ভ্যান জোগাড় ক’রে এনেছে চিনু শর্মার জন্য। বস্তিতে মাঝেমধ্যে ঝগড়া হলেও, বিপদে সবাই সবার পাশে দাঁড়ায়। অ্যাম্বুলেন্সের জন্য তারা অপেক্ষা করে না। তারা গায়ে-গতরে খেটে বিপদের মোকাবিলা করে বিপদের।
গুল্লু তার বাবাকে নিয়ে ভ্যানের পেছনে চেপে বসল। আর, পুঁটি চালিয়ে নিয়ে গেল পলাশপুর সরকারি হাসপাতালে।
(৭)
সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কেউ এগিয়ে আসেনি গুল্লুর জন্য। তার পাশের দোকানদারেরা, তার বস্তির লোকজন এবং তার পরিবার আছে বটে, কিন্তু গুল্লুর সমস্যার সমাধান তাদের সামর্থ্যের বাইরে। ডাক্তার সেন অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জুনিয়র ডাক্তারকে এখনও সমাজের উচ্চবিত্তরা সেইভাবে পাত্তা দেন না!
“শালা, দোগলা দুনিয়া…হারামি শালা…দোগলা ইনসান…”-- হঠাৎ গুল্লু নিজের মনেই এই কথাগুলো আওড়ালো।
তার পাশে বসা পুঁটিরাম গুল্লুর কাঁধে হাত রাখল। গুল্লু আশা ছেড়ে দিয়েছে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। চিনু শর্মার মৃত্যু এখন সময়ের অপেক্ষা। ডাক্তার সেন রক্ত জোগাড় করার জন্য এদিক সেদিক দৌড়োচ্ছেন। কিন্তু, শেষ রক্ষা করা গেল না। চিরপুরাতন নিয়মে টাকার অভাবে, ক্ষমতার অভাবে শেষ হ’য়ে গেল একটা প্রাণ। বয়স যতই বেশি হোক, এইভাবে মেরে দেওয়ার অধিকার কেউ কী দিয়েছে সমাজকে? আর জোয়ান ছোকরা হলেও কী সমাজ বদলে দিত নিজের নিয়ম? নাহ, কখনোই না। সমাজ বরাবরের ভণ্ড। সামনে এক, পেছনে আরেক। ডাক্তার সেন একটা শববাহী গাড়ি ঠিক ক’রে দিলেন। মনে মনে ভাবলেন, “চিনু শর্মা মারা গেলেন গরীবের মতো, কিন্তু সৎকারটা অন্তত রাজার মতো হোক।”
গুল্লু তার বাবার ব্যান্ডেজে জড়ানো মাথায় একটা চুমু খেয়ে বলল, “আপকা ইস হারামি অউলাদ কো মাফ কর দিজিয়ে, বাবুজি। শালা, দোগলা দুনিয়া আপকো জিনে নেহি দিয়া।”
তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার ক’রে বলল, “উন সব কো ভি চ্যায়েন সে জিনে নেহি দেনা ভগওয়ান।”
কাঁদতে কাঁদতে বাকরুদ্ধ গুল্লু এবং তার সহমর্মীরা চলল চিনু শর্মার শব নিয়ে। এই মৃত্যু তাদের কথা কেড়ে নিয়েছে। শুধু, কিছুজনের মুখে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, “রাম নাম সত্য হ্যায়”।
পথেই পড়ল দেবব্রত রায়ের বাড়ি। হঠাৎ, গুল্লু ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে মাটি থেকে তুলে নিল ঢিল। তারপর, সেই ঢিলে নিজের ঘেন্না ভরা থুতু দিয়ে ছুঁড়ে মারল ঢিল দেবব্রত রায়ের বাড়িতে। জানালা খোলা থাকায় ঢিল দোতলার ঘরের ভেতরে ঢুকে ভেঙে দিল কাচের আয়না। ঝনঝন শব্দে কেঁপে উঠল ঘর। প্রথমে দেবব্রত রায় বুঝে উঠতে না পারলেও, পরে বাইরে বেরিয়ে এলেন, “কোন স্কাউন্ড্রেল?”, বলতে বলতে। কিন্তু, আচমকা এই ঘটনা ঘটায় আর দেবব্রত রায়ের নিজেকে সামলে বেরিয়ে আসতে সামান্য দেরি হওয়ায়, ভিড় মিশে গেছিল দূরে। দেবব্রত রায় খুব ভালোভাবে বুঝতে পারেননি ব্যাপারটা। শুধু, সেদিন গুল্লুর ছোঁড়া ঢিলে ভেঙে গেছিল একটা আয়না। দেবব্রত রায়ের আয়না আসলে এই ভণ্ড সমাজের দর্পণ। এই আয়নাই বিভেদ ক’রে রেখেছে উঁচু-নিচুর। আর তাই এটাই ছিল গুল্লুর প্রতিবাদের প্রকাশ। কারণ, নাপিতের সাথে আয়নার সম্পর্ক যে খুব গভীর। এর বেশি আর কীই বা করতে পারে গুল্লু? পরের প্রজন্ম ওরই ভরসায় ব’সে আছে যে!